রাঘববাবুর বাড়ি – শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
১. পুরুতমশাই নন্দলাল ভট্টাচার্য
সকালবেলায় পুরুতমশাই নন্দলাল ভট্টাচার্য রাঘব চৌধুরীর বাড়ির নিত্যপূজা সেরে বেরোচ্ছেন। হঠাৎ নজরে পড়ল বাইরের দিককার বাগানে একটা মুশকো চেহারার লোক উবু হয়ে বসে বাগানের কাঁটাতারের বেড়া মেরামত করছে। মুখটা ভারী চেনা-চেনা ঠেকল। এ গাঁয়ের লোক নয়, তবে কোথাও একে দেখেছেন।
নন্দলালের টিকিতে একটা কলকে ফুল বাঁধা, গায়ে নামাবলী, বাঁ বগলে ছাতা, ডান হাতে সিধের পুঁটুলি, পরনে হেঁটো ধুতি, পায়ে খড়ম। দেখলেই মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা হওয়ার কথা। হয়ও। নন্দলালকে দেখলেই লোকে একটু তটস্থ হয়ে পড়ে।
নন্দলাল দু পা এগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “ওহে বাপু, মুখোনা বড্ড চেনা-চেনা ঠেকছে যে!”
অন্য কেউ হলে তাড়াতাড়ি উঠে হাতজোড় করে বলত, “পেন্নাম হই ঠাকুরমশাই” কিংবা, “পাতঃ পেন্নাম বাবাঠাকুর”, বা যা হোক ওরকম কিছু। এ লোকটা সেই ধার দিয়েই গেল না। দু’খানা জ্বলজ্বলে চোখে একবার তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিক্ষেপ করে বলল, ‘চেনা-চেনা ঠেকলেই যে চিনতে হবে তেমন কোনও কথা আছে?
লোকটা যে ঠ্যাটা এবং তিরিক্ষে, তা বুঝে নন্দলাল একটু দমে গেলেন। চেহারাখানা দেখে ষণ্ডাগুণ্ডা বলেই মনে হয়। ডাকাত বা খুন খারাপির আসামি হওয়াও বিচিত্র নয়। কথা হল, রাঘব চৌধুরীর বাড়িতে এসে জুটলই বা কী করে! আর এক কথা, লোকটাকে তিনি কোথাও দেখেছেন, কিন্তু কোথায় তা মনে পড়ছে না।
রাঘব চৌধুরী বড়লোক হলে কী হয়, ভারী খামখেয়ালি মানুষ। পাট আর গুণচটের পৈতৃক কারবারে লাখো-লাখো টাকা কামান বটে, কিন্তু লোকটার বাস্তববুদ্ধির একটু অভাব আছে। নইলে এ বাড়িতে যেসব লোক এসে জোটে, দূরদর্শী হলে কদাচ তাদের আশ্রয় দিতেন না।
পালোয়ান হাবু দাসের কথাই ধরা যাক। একসময়ে নাকি কুস্তি টুস্তি করত। রাঘববাবুর কাছে একদিন এসে ধরে পড়ল, “হুঁজুর, গতরখানা তো দেখেছেন। এই দেহের খোরাকটা একটু বেশিই। কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে তাতে দু’বেলা ভরপেট জোটানোই মুশকিল, যদি একটু আশ্রয় দেন তা হলে যা করতে বলবেন, করব।”
রাঘববাবু বললেন, “আহা, কুস্তিগির তো একজন আমিও খুঁজছি, তা ভালই হল। আমার ছেলেপুলেগুলোকে শেখাও, আমিও মাঝেমধ্যে একটু-আধটু তালিম নেব’খন।”
তা হাবু দাস থেকে গেল। তার জন্য একটা আখড়াও তৈরি করে দিলেন রাঘববাবু। তাঁর দুই ছেলে প্রথম প্রথম উৎসাহের চোটে কুস্তি শিখতে লেগে পড়ল। কিন্তু দিনদুয়েক বাদেই গায়ের ব্যথায় দুইজনকে শয্যা নিতে হল। রাঘববাবুর গিন্নি বললেন, “ওদের হল নরম শরীর, দুধননী খেয়ে মানুষ, ওদের কি ওসব আসুরিক কাণ্ড সহ্য হয়! কবে কোনটার ঘাড় মটকে যায়, হাত বা পা ভাঙে, দরকার নেই বাবা কুস্তি শিখে। বাছারা আমার ননীর পুতুল হয়েই থাকুক।”
তা তাই হল। রাঘববাবুও একদিন কি দু’দিন ল্যাঙট এঁটে নেমেছিলেন বটে, কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি। কয়েকদিন বাদেই হাবুর আখড়া ফাঁকা হয়ে গেল। তা হাবু তখন একা-একাই মুগুর ভাঁজত, ডন বৈঠক করত। কিন্তু কিছুদিন পরে তারও উৎসাহে ভাঁটা পড়ে গেল। এখন হাবু দাসের মাত্র দুটো কর্ম, খাওয়া আর ঘুমনো। অ্যাই বিরাট চেহারা হয়েছে, মস্ত ভূঁড়ি, শরীরে চর্বি থলথল করছে। দিনরাত ঘুমোলে আর রাশি রাশি খেলে যা হয়। কুস্তি দূরস্থান, এখন দশ পা হাঁটতেও তার হাঁফ ধরে।
ওই যে কালোয়াত গুণেন সাঁতরা, মস্ত নাকি গাইয়ে, কিন্তু গাঁ-গঞ্জে সমঝদার না পেয়ে একদিন সভাগায়ক হবে বলে রাঘববাবুর কাছে এসে হাজির।
রাঘববাবু সব শুনে তটস্থ হয়ে বললেন, “আজ্ঞে, আমি তো রাজা জমিদার নই, আমার সভা-টভাও নেই, কাজেই সভাগায়ক রাখার কথাই ওঠে না। আমি নিকষ্যি ব্যবসাদার।”
গুণেন ভারী মুষড়ে পড়ে বলল, “তবে যে সবাই বলছিল আপনার কাছে এলেই নাকি একটা হিল্লে হবে?”
রাঘববাবু কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, “আজ্ঞে, কালোয়াতি গানও আমি বুঝি না। বড়জোর কেত্তন বা শ্যামাসঙ্গীত অবধি আমার দৌড়, তবে গুণী মানুষের কদর আমি বুঝি। এসে যখন পড়েছেন তখন তো আর ফেলতে পারি না।”
তা গুণেনও থেকে গেল। প্রথম প্রথম ভোররাতে উঠে খুব রেওয়াজ-টেওয়াজ করত। সেই আওয়াজে গঞ্জের যত কুকুর এসে রাঘববাবুর সদরে জুটে সে কী ঘেউ-ঘেউ! তার মানে এ নয় যে গুণেন কিছু খারাপ গাইত, কিন্তু এলাকায় কুকুরগুলোেই বজ্জাত বেরসিক। বিরক্ত হয়ে গুণেন রেওয়াজ প্রায় ছেড়েই দিল। এখন তাস-পাশা খেলে সময় কাটায়। মাঝে-মাঝে একটু-আধটু গুনগুন করে।
ওই যে লম্বা, সুড়ঙ্গে, সুটকো চেহারার ভূতনাথ হালদার, সে নাকি একজন ভূত-বিশারদ। যত বুজরুক সব এসে এই রাঘবের ঘাড়ে ভর করে। ভূতনাথ নাকি ভূতবিদ্যা গুলে খেয়েছে। তার চারদিকে সর্বদাই ভূতের ভিড়! বছরটাক আগে এসে সেও জুটে গেল এ বাড়িতে। রাঘবকে বলল, “বাবুমশাই, ভূত বড় ত্যাঁদড় জিনিস, এমনিতে টেরটি পাবেন না। কিন্তু ধরুন চিতল মাছের পেটি দিয়ে পরিপাটি ভাত খাবেন বলে মনস্থ করলেন, একটা দুষ্টু ভূত এক খাবলা নুন দিয়ে গেল ঝোলে।”
রাঘব সায় দিয়ে বললেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম তো হয়ই।”
“তারপর ধরুন শুভকার্যে বেরোচ্ছেন, দুর্গা দুর্গা বলে বেরোতে পা বাড়িয়েছেন, একটা বদমাশ ভূত টক করে খুতির খুঁটটা দিল পায়ে জড়িয়ে। দড়াম করে পড়লেন আর কী। ভূতের কাজ বলে টেরটিও পেলেন না।”
রাঘব সোৎসাহে বললেন, “ঠিক বলেছেন তো! গত বছর আমার তো একবার এরকম হয়েছিল।”
“শুধু কি তাই বাবুমশাই! ধরুন, আপনার শুদ্ধাচারী বিধবা শাশুড়ি একাদশীর পরদিন চারটি ভাত পাথরের থালায় বেড়ে নিয়ে খেতে বসেছেন, একটা শয়তান ভূত টুক করে একখানা মাছের কাঁটা তার পাতে ফেলে গেল। কী সর্বনাশ বলুন তো!”
রাঘব মাথা নেড়ে বললেন, “হ্যাঁ, এরকম তো হতেই পারে। হয়ও।”
“আর চিন্তা নেই মশাই। আজ থেকে এই শৰ্মা গ্যাঁট হয়ে বসল এই বাড়িতে। ত্রিসীমানায় আর ভূতের উপদ্রব থাকবে না।”
রাঘববাবু তাঁর পুরনো কাজের লোক নবকৃষ্ণের দিকে চেয়ে বললেন, “কী রে নবু, এরকম একজন তোক বাড়িতে থাকা তো ভালই, কী বলিস?”
নবকৃষ্ণ রাঘববাবুর তামাক সেজে কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে গড়গড়ার মাথায় বসাচ্ছিল। খুব নির্বিকার গলায় বলল, “ওঝা-বদ্যি রাখুন তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু তা হলে পীতাম্বরমশাই, হরুখুড়ো, পঞ্চা বিশ্বেস, আন্নাকালী দেব্যা এদের কী ব্যবস্থা হবে? তেজালো ওঝা দেখলে তাঁরা কি ভড়কে যাবেন না?”
রাঘব খুবই চিন্তিত হয়ে তামাক টানতে টানতে বললেন, “হ্যাঁ, সেটাও তো একটা কথা! ওঝা ঢুকলে তাঁরা যদি যাতায়াত বন্ধ করে দেন তা হলে তো সর্বনাশ!”
ভূতনাথ হাঁ করে দু’জনের কথা শুনছিল। বড় বড় চোখ করে বলল, “আপনারা কাদের কথা কইছেন? এরা সব কারা?”
রাঘব তামাক টানতে টানতে নিমীলিত চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে বললেন, “এঁরা এ বাড়ির পুরনো আমলের মানুষ সব। পীতাম্বরমশাই আর হরুখুড়ো আমারই ঊর্ধ্বতন পঞ্চম আর সপ্তম পুরুষ। পঞ্চা বিশ্বেস এ বাড়িতে দেড়শো বছর আগে কাজ করত, এইনবকৃষ্ণেরই ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ, আন্নাকালী দেব্যা ছিলেন আমার ঠাকুর্দার বিধবা পিসি। আনাচে কানাচে থাকেন, সারা বাড়িতে ঘুরঘুর করেন।”
নবকৃষ্ণ বলল, “এঁরা তো আছেই, তা ছাড়া পালে পার্বণে আরও অনেকে এসে জুটে যান। তাই বলছিলাম, ওঝাবদ্যি বসান দিলে এঁরা কুপিত হয়ে যদি তফাত হন তা হলে কি বাড়ির মঙ্গল হবে?”
ভূতনাথ ভারী ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে বলল, “ওরে বাবা! তাঁরা কি দেখাটেখাও দেন নাকি গো নবুদাদা?”
“তা দেবেন না কেন? নিত্যিই দেখছি। একটু আগেই তো গোয়ালে সাঁজাল দিতে গিয়ে পীতাম্বরমশাইকে দেখলুম, কেলে গোরুটার গলায় হাত বুলিয়ে আদর করছেন?”
ভূতনাথ কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, “বাপ রে! এ বাড়িতে তো তা হলে ভূতের মচ্ছব।”
নবকৃষ্ণ বলল, “উঁহু, উই, ভূত বললে এঁদের ভারী অপমান হয়। হেঁদো ভূত তো নন। দেয়াল করতেও আসেন না। বাড়ির মঙ্গলামঙ্গলের কথা চিন্তা করেই চারদিকে নজর রাখেন আর কী!”
শুনে ভূতনাথ ভিরমি খায় আর কী! মাথায় জলটল দিয়ে তাকে সুস্থ করার পর রাঘববাবু বললেন, “তোমার ভয় নেই হে, আমার বাড়িতে যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই নিপাট ভাল লোক। শুধু ওই আন্নাঠাকুমাই যা একটু খাণ্ডার। তাকে না ঘাঁটালেই হল। যা রে নবু, ওকে ব্যারাকবাড়ির পুবদিকের ঘরখানায় বন্দোবস্ত করে দে।”
তা ভূতনাথও রয়ে গেল। এভাবেই এক-একজন এসে ঢুকে পড়ে এ বাড়িতে। তারপর আর নড়তে চায় না। বৈজ্ঞানিক হলধর হালদার একসময়ে কালিকাপুর ইস্কুলে বিজ্ঞানের মাস্টার ছিলেন। মাথাপাগলা মানুষ। ইস্কুল কামাই করে বাড়িতে বসে নানারকম উদ্ভট বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতেন। শেষে ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ বিরক্ত হয়ে তাঁকে চাকরি থেকে ছাড়িয়েই দিল। বিপাকে পড়ে তিনিও এসে একদিন জুটে গেলেন রাঘবের বাড়িতে। এদের জন্যই বাড়ির লাগোয়া একটা ব্যারাকবাড়ি করে রেখেছেন রাঘববাবু, কম করেও পঁচিশ-ত্রিশখানা ঘরে নানারকম লোক থাকে। বেশিরভাগই নিষ্কর্মা, কারও কারও নানা বাই-বাতিক, কেউ কেউ ভণ্ডুলকর্মা, অর্থাৎ বৃথা কাজে সময় কাটান।
রাঘববাবুর এই যে অজ্ঞাতকুলশীল উটকো লোকদের আশ্রয় দেওয়া, এটা বাড়ির লোকেরা মোটেই ভাল চোখে দেখে না। কিন্তু তাঁকে বলে বিশেষ লাভ হয় না। বড়ই দয়ার শরীর। লোকে যা বলে তাই বিশ্বাস করে বসেন। কিছুদিন আগে পিছনের বাগানের আগাছার জঙ্গলে একজন লোককে পড়ে থাকতে দেখে বাগানের মালি চেঁচামেচি শুরু করে। লোকটাকে তুলে এনে মুখেচোখে জল থাবড়ানোর পর সে জ্ঞান ফিরে পেয়ে যা বলল তা আষাঢ়ে গল্প। সে নাকি এই পৃথিবীর লোক নয়। অনেক দূরে অন্য এক নীহারিকায় এক গ্রহে তার বাস। মহাকাশযানে তারা ভুল পথে এদিকে এসে পড়ে। তার সঙ্গীরা নাকি ষড়যন্ত্র করে তাকে এখানে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে। গ্রহান্তরের লোকের বাংলা ভাষা জানার কথা নয়, পরনে ধুতি আর জামা থাকারও কথা নয়। ভেতো বাঙালির মতো চেহারাই বা তার হবে কেন? কেউ তার কথা বিশ্বাস করল না বটে কিন্তু রাঘববাবু খুঁতখুঁত করতে লাগলেন, আহা, হতেও তো পারে। দুনিয়ায় কত কী-ই না ঘটে, কেষ্টর জীব, ফেলতে তো পারি না।
তা সেই গুলবাজ গোলাপ রায়ও দিব্যি বহাল তবিয়তে ব্যারাকবাড়িতে গদিয়ান হয়ে বসেছে।
কিন্তু এই নতুন অভদ্র লোকটা নন্দলালকে খুব ভাবিয়ে তুলল। তিনি ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে ভিতরবাড়িতে গিয়ে নবকৃষ্ণের ঘরে হাজির হলেন। নবকৃষ্ণ এ-বাড়ির ম্যানেজার। এ-বাড়ির সবকিছু দেখভাল করার ভার তার ওপর। দশ-বারোজন চাকর আর গুটি আট-দশ ঝি তারই অধীনে দিনরাত খাটে। বছর চল্লিশেক বয়সের নবকৃষ্ণকে বিবেচক মানুষ বলেই মনে হয় নন্দলালের।
নন্দলালকে দেখে নবকৃষ্ণ শশব্যস্তে উঠে বলল, “ঠাকুরমশাই যে! পেনাম হই, পেন্নাম হই।”
“ওহে নবকৃষ্ণ, আমি তো পরিস্থিতি ভাল বুঝছি না। ওই ডাকাতের মতো চেহারার লোকটা কোথা থেকে উদয় হল বল দেখি! ও তো খুনিয়া লোক। এসব লোককে কি বাড়িতে ঠাঁই দিতে আছে? এ তো বিছানায় কেউটে সাপ নিয়ে ঘুমনো!”
নবকৃষ্ণ ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে বলল, “কর্তা কি কারও বুদ্ধি বা পরামর্শ নেন? বলে বলে তো মুখ পচে গেল মশাই। গতকাল সন্ধেবেলায় ওই ঘটোৎকচটি এসে উদয় হলেন। গুলবাজের মতো চেহারা, ভাঁটার মতো চোখ, কথা কয় না গর্জন করে বুঝে ওঠা মুশকিল। মস্ত নাকি লেঠেল। হাতে দু’খানা তেলচুকচুকে লাঠিও ছিল। তা আমি বললুম, কামশাই, আমদের কি লেঠেলের অভাব? কাহারপাড়ায় একশ’ লেঠেল মজুত, এক ডাকে এসে হাজির হবে। কর্তামশাই খুঁতখুঁত করতে লাগলেন, ওরে, হাতের কাছে একজন লেঠেল থাকাও ভাল। এ লোকটাকে দেখে গুণী মানুষই তো মনে হচ্ছে। একে রাখলে বাড়ির ছেলেপিলেগুলোও একটু লাঠি খেলাটেলা শিখতে পারে, আমাদেরও একটু বলভরসা হয়। আমি আর বেশি কিছু বলতে ভরসা পেলুম না, লোকটা মানুষখেকো চোখে এমনভাবে আমার দিকে চাইছিল যে, গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল বড্ড।”
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নন্দলাল বললেন, “কর্তাবাবু আর যেগুলোকে জুটিয়েছেন সেগুলো অকালকুণ্ড বটে, কিন্তু ভয়ঙ্কর নয়। কিন্তু এটি তো সুবিধের লোক বলে মনে হচ্ছে না হে। যেমন চেহারা তেমনই ব্যবহার। একটু নজর রাখিস বাবা, যন্তরটিকে কোথায় যেন দেখেছি, কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না। নামটাম কিছু বলেছে?”
“যে আজ্ঞে। কদম দাস। চক হরিপুরে বাড়ি।”
নামটা চেনা ঠেকল না নন্দলালের। চক হরিপুর কোথায় তাও জানেন না, তবে এসব পাজি লোকের মুখের কথায় বিশ্বাস কী!
“দুর্গা দুর্গতিনাশিনী” বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নন্দলাল খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন। সামনে দিয়ে যেতে কেমন যেন সাহস হল না।
খিড়কির দিকে পুকুর। পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিল গোলাপ রায়।
তাঁকে দেখে বিগলিত হাসি হেসে বলল, “ঠাকুরমশাই যে! তা পুজো সেরে এলেন বুঝি?”
নন্দলাল রোষকরিত লোচনে গুলবাজটার দিকে চেয়ে বললেন, “চ্ছ।”
গোলাপ রায় হাসতে হাসতে বলল, “ওঃ, আমাদের মকরধ্বজ গ্রহে যদি একবার যেতেন ঠাকুরমশাই, তা হলে আপনার পুজোপাঠের খুব সুবিধে হয়ে যেত।”
নন্দলাল গম্ভীর গলায় বললেন, “কীরকম?”
“আরে মকরধ্বজের কাছেই তো ইন্দ্রলোক কিনা। আমরা তো মাঝে-মাঝেই দেখতে পাই সাঁ করে একটা পুষ্পকরথ বেরিয়ে গেল, কিংবা বাঁই করে নারদের টেকি চলে গেল। নিশুত রাতে কান পাতলে তো ইন্দ্রের সভার নাচগানের শব্দও পাওয়া যায়। নূপুরের শব্দ, তবলার বোল, সুরেলা গলার গান, এমনকী কী বলব মশাই, কতদিন ইন্দ্রলোক থেকে ফেলা তরকারি আর ফলের খোসা আমাদের উঠোনে এসে পড়েছে।”
নন্দলাল কটমট করে তাকিয়ে গোলাপ রায়কে ভস্ম করে দেওয়ার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন, “বটে?”
“তবে আর বলছি কী মশাই! তারপর ধরুন পুজোপার্বণে আপনারা মাটির মূর্তি গড়ে পুজোটুজো করেন। সেদিক দিয়ে আমাদের ভারী সুবিধে। মূর্তিটুর্তির বালাই নেই। যার পুজো হয় তিনিই টুক করে নেমে এসে পুজো নিয়ে চলে যান। গণেশবাবাকে ডাকলেন তোত উনি ধেড়ে ইঁদুরটাকে নিয়ে হেলতে দুলতে এসে হাজির। দিব্যি শুড় দিয়ে চালকলা সাপটে খেয়ে ঢেকুর তুলে উঠে পড়লেন। আমি একবার গণেশবাবার ইঁদুরের লেজ ধরে টেনেছিলাম বলে ইঁদুরটা এমন কামড় দিল, এই দেখুন ডান হাতে এখনও সেই কামড়ের দাগ। তারপর ধরুন মা-সরস্বতী, দিব্যি বীণা বাজাতে বাজাতে হাঁসের পিঠে চড়ে নেমে এলেন। পুজো নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ইংরিজি, বাংলা, অঙ্কও কখনওসখনও দেখিয়ে দেন। তবে আমাদের আসল সমস্যা হয় দুর্গাপূজার সময়। ছেলে, মেয়ে, সিংহ, সাপ, অসুর নিয়ে মা যখন নামেন তখন একেবারে গলদঘর্ম অবস্থা, তার ওপর সিংহটা গাঁক গাঁক করে ডাক ছেড়ে এর ঘাড়ে ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে চায়। অসুরটা ফাঁক বুঝে পালানোর চেষ্টা করে। সাপটা তেড়েফুড়ে কাকে কামড়ায় তার ঠিক নেই। তার ওপর হাঁস প্যাঁচা ইঁদুর ময়ূর সকলে মিলে এক ঝটাপটি অবস্থা। মা দুর্গার দশটা হাত কেন তা আমাদের মকরধ্বজ গ্রহে গেলে বুঝবেন ঠাকুরমশাই। মনে হবে দশটা হাতেও কুলোচ্ছে না। গোলমালে চণ্ডীমণ্ডপ ভেঙে পড়ে আর কী! চারদিন আমাদের নাওয়া খাওয়া ভুলে সামাল দিতে হয়।”
গুরুগম্ভীর মুখ করে নন্দলাল বললেন, “তা হলে তো তোমাদের গ্রহেই যেতে হয় হে।”
একগাল হেসে হাতজোড় করে গোলাপ রায় বলল, “যে আজ্ঞে। বেড়াতে বেড়াতে চলে আসুন একবার। বেশি দূরও নয়, মাত্র আড়াই লক্ষ লাইট ইয়ার। খুব সুবিধে হবে আপনার। মকরধ্বজে আবার অমাবস্যা পুন্নিমে নেই বলে আরও সুবিধে।”
“কেন হে বাপু, সেখানে অমাবস্যা পুন্নিমে নেই কেন?” গোলাপ চোখ গোল করে অবাক হয়ে বলে, “অমাবস্যা পুন্নিমে হওয়ার কি জো আছে মশাই? আমাদের আকাশে একুনে একুশখানা চাঁদ। তা ধরুন কম করেও রোজ রাতে দশ থেকে বারোখানা চাঁদ থাকে মাথার ওপর। অমাবস্যাটা হবে কী করে বলুন? জ্যোৎস্নার ঠেলায় পাগল হওয়ার জোগাড়। দিনে রাতে তফাত করাই মুশকিল। আমার মেজোমামার কথাই ধরুন। ভুলোমনের মানুষ। রাত দেড়টায় দুপুর মনে করে পুকুরে নেয়ে এসে পাতপিড়ি করে বসে হাঁক দিলেন, কই গো, ভাত বেড়ে আনো। মামি তখন ঘুম থেকে উঠে হাই তুলতে তুলতে এসে বললেন, আ মরণ! মিনসের ভীমরতি হল নাকি? বলে নড়া ধরে তুলে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।”
নন্দলাল হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললেন, “না হে বাপু। তোমার সঙ্গে এঁটে ওঠাই মুশকিল। গল্প উপন্যাস লিখলে তো শরৎবাবুর মতো নাম করতে পারতে হে। এমন প্রতিভা নষ্ট করছ?”
হঠাৎ গোলাপ রায় চোর-চোখে চারদিকটা একটু দেখে নিয়ে গলাটা খাটো করে বলল, “একখানা কথা ছিল ঠাকুরমশাই।”
“বলে ফেলল।”
“সকাল থেকেই বড্ড আপনার কথাই মনে হচ্ছে, ভাবছিলাম, ঠাকুরমশাইয়ের মতো এমন বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোক এই অজ পাড়াগাঁয়ে আর কেই বা আছে। কপালের ফেরে পড়ে আছেন বই তো নয়। শহর গঞ্জে গিয়ে পড়লে আপনার সত্যিকারের কদর হত।”
“সে না হয় বুঝলুম, কিন্তু কথাটা কী?”
“একটু গুহ্য কথা মশাই, পাঁচকান করবেন না।”
“সে ভয় নেই। পাঁচকান করা আমার স্বভাব নয়।”
গলাটা আরও খাটো করে গোলাপ রায় বলল, “তা বলছিলাম কী, কর্তাবাবু যে একজন সাঙ্ঘাতিক গুণ্ডাকে ভাড়া করে এনেছেন সে খবর রাখেন কী? সাত ফুটের কাছাকাছি লম্বা আর এই আলিসান তাগড়াই চেহারা। কপাল খারাপ বলে ভাগ্যের দোষে না হয় এসেই পড়েছি মশাই, তা বলে গুণ্ডা দিয়ে পেটাই করা কি ভাল? শত হলেও অতিথি নারায়ণ বলে কথা! ভালয় ভালয় বললে কি তল্পিতল্পা গুটিয়ে বিদেয় হতুম না!”
নন্দলাল গম্ভীর হয়ে বললেন, “গুণ্ডাটা তোমাকে কিছু বলেছে বুঝি?”
মাথা নেড়ে গোলাপ রায় বলল, “আজ্ঞে না। বলা কওয়ার লোকও নয়। এ হল কাজের লোক। শুধু দু’খানা চোখ দিয়ে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিচ্ছে, সে কী রক্তজলকরা চাউনি মশাই! পাঁচু বলছিল কর্তাবাবু নাকি মেলা খরচাপাতি করে গুণ্ডাটাকে ভাড়া করে এনেছেন। শুনে তো কাল রাতে মুখে ভাতই রুচল না। সোনামুগের ডাল আর বেগুন ভাজা ছিল মশাই, সবই প্রায় ফেলে উঠে পড়লুম। গুণ্ডাটা আমার মুখোমুখি বসে মাঝে মাঝে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যে, পেটভরে খেতে সাহসই হল না। তাই বলছিলুম ঠাকুরমশাই, গুণ্ডাটা কি আমার জন্যই আনা করালেন কর্তাবাবু?”
নন্দলাল গম্ভীর হয়ে বললেন, “কিছুই বলা যায় না হে, দিনকাল যা পড়েছে।”
‘বড় ভয়ের কথা হল মশাই, মকরধ্বজের গাড়িরও তো এসে পড়ার কথা ছিল। তা সেও এল না। বেঘোরে প্রাণটা গেলে বাড়ির লোক যে খবরটাও পাবে না। শ্রাদ্ধশান্তিরই বা কী ব্যবস্থা হবে কে জানে! উইল টুইলও করে রাখিনি মশাই। তারপর ধরুন, অপঘাতে মৃত্যু। এখানে তো এমন কেউ নেই যে, গরজ করে গিয়ে গয়ায় পিণ্ডটা দিয়ে আসবে।”
একটু ভেবে নন্দলাল বললেন, “অত আগ বাড়িয়ে ভাবা কেন হে? মারলে থানা-পুলিশ হবে, একটু-আধটু কিল, চড়চাপড় বা রদ্দাটদ্দা দিতে পারে বড়জোর। তা ওসব তেমন গায়ে না মাখলেই হল। একটু নজর রেখে চলো, আমি দেখছি।”
“ভরসা দিচ্ছেন ঠাকুরমশাই?”
“দিচ্ছি। ঘাবড়ানোর কিছু নেই।”
“আপনিই বল-ভরসা,” বলে গোলাপ রায় নন্দলালের পায়ের ধুলো নিয়ে ফেলল।
চিন্তিত মুখে নন্দলাল পুকুরধারের রাস্তাটা ধরে এগোচ্ছেন, হঠাৎ পিপুল গাছের আড়াল থেকে রোগামতো দাড়িগোঁফওলা, লম্বা চুলের একজন লোক বেরিয়ে এসে পথ জুড়ে দাঁড়াল।
“ঠাকুরমশাই যে!”
লোকটাকে দেখে নন্দলাল বিশেষ খুশি হলেন না। লোকটা ঘোর নাস্তিক, বৈজ্ঞানিক হলধর হালদার।
নন্দলাল কঠিন গলায় বললেন, “তোমার আবার কী চাই?”
হলধর চাপা গলায় বলল, “ওই গুলবাজটা কী বলছিল বলুন তো আপনাকে! ওর একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না। ব্যাটা নাকি গ্রহান্তরের মানুষ, ওদের বিজ্ঞান নাকি পঞ্চাশ হাজার বছর এগিয়ে আছে! বলেনি আপনাকে?”
“তা বলেছে বটে।”
“বিশ্বাস করেছেন নাকি ওর কথা?”
“দ্যাখো বাপু, আমি পুজোআচ্চা নিয়ে থাকি, বিজ্ঞান-টিজ্ঞানের আমি কীই বা বুঝি! তবে যা-ই বলো, গুল মারলেও লোকটা তোমার মতো নাস্তিক নয়, ঠাকুর-দেবতাকে মান্যি-গণ্যি করে। ধর্মে মতি আছে।”
“খুব চিনেছেন তা হলে! ধর্মে মতি না হাতি, ও আসলে একটা স্পাই।”
নন্দলাল অবাক হয়ে বলেন, “বলো কী হে? এই অজ পাড়াগাঁয়ে স্পাই ঘোরাঘুরি করবে কেন? এখানে সুলুকসন্ধান করার মতো আছেটাই বা কী?”
হলধর বিরস মুখে বলল, “আছে মশাই, আছে, আর সেইটেই তো দুশ্চিন্তার কারণ। আমার অমন আবিষ্কারটা যদি শত্রুপক্ষের হাতে চলে যায় তা হলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে, পনেরো বছরের সাধনা। এ দেখছি তীরে এসে তরী ডোবার আয়োজন।”
নন্দলাল নাক সিটকে বললেন, “তা কী এমন হাতি-ঘোড়া আবিষ্কার করলে হে? শুনতে তো পাই সারাদিন ঘর বন্ধ করে শিশিবোতল কৌটো বাউটো দিয়ে কীসব খুটুর-মুটুর করো, তা শিশিবোতল থেকে কি বেহ্মদত্তি বেরোল নাকি?”
হলধর ভ্রু কুঁচকে নন্দলালের দিকে চেয়ে বলল, “ও বিদ্যে বোঝার মতো ক্ষমতা আপনার ঘটে নেই, স্পাই কি এই ধ্যাধেরে গোবিন্দপুরে এমনি আসে মশাই? কাঁঠাল পাকলেই ভোমা মাছি এসে জোটে, দেখেননি? এও হচ্ছে সেই ব্যাপার।”
নন্দলাল মাথা নেড়ে ভালমানুষের মতো বললেন, “শুনেছি বটে এক যোজন দূরে গোরু মরলেও নাকি গৃধিনীর ঝুঁটি নড়ে, তা তোমার থলি থেকে কী ম্যাও বেরোল?”
রোষকষায়িত লোচনে নন্দলালের দিকে চেয়ে হলধর বলল, “শুনতে চান? শুনলে মুখের হাসি কিন্তু শুকিয়ে যাবে। এসব তো ঠাট্টা মশকরার জিনিস নয়, অং বং দুটো মন্তর বলে দুটো ফুল ফেলে দিয়ে চাল কলা আর দক্ষিণা আদায়ের ফাঁকিবাজি কারবারও নয়, বিজ্ঞান হল সাধনা আর হাড়ভাঙা খাটুনি।”
নন্দলাল মিষ্টি করে হেসে বললেন, “খাটুনির কথা বলছ বাপু?” তা আমাদের ওই ন্যালা পাগলাকে দ্যাখো না, সারাদিন কী খাটুনি না খাটছে। এই সারা গায়ে হরিবোল হরিবোল বলে দৌড়ে বেড়ালোলা, এই তালগাছে উঠে গেল, এই কাকবকের সঙ্গে ঝগড়া করতে লাগল, এই ছেলেপুলেদের তাড়া করল, এই আকাশে ঢিল ছুঁড়তে লাগল, এই ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে এল, তারও কি খাটুনির শেষ আছে?”
‘অ! আপনারও তা হলে ধারণা যে, আমি পাগল? তবে জেনে রাখুন, আর্কিমিডিস, গালিলেওকেও লোকে পাগল বলেই মনে করেছিল একদিন। প্রতিভা আর পাগলামির তফাত বুঝতে এলেম চাই, বুঝলেন মশাই? এই আপনাদের মতো লোকেরা অন্ধ বিশ্বাসে আর কুসংস্কারে দেশটাকে ডুবিয়ে দিচ্ছেন বলেই এদেশে বিজ্ঞানের উন্নতি হল না।”
নন্দলাল চটলেন না। মোলায়েম গলাতেই বললেন, “ওরে বাবা, আমাদের ন্যালা পাগলাও কি যে-সে লোক নাকি? তাকেও তো অনেকে ছদ্মবেশী সাধক, অনেকে শিবের অবতার বলে মনে করে। খামোখা চটে যাও কেন বলো তো? ইতিবৃত্তান্তটা একটু খুলে বলো দেখি শুনি।”
হলধর একটা শ্বাস ফেলে বলল, “যারা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করে আমি তাদের পছন্দ করি না বটে, কিন্তু আপনাকে আমার একজন বিবেচক মানুষ বলেই মনে হয়েছিল। লোকে বলে আপনি নাকি বেশ বুদ্ধিমান লোক, বিপদে পড়লে লোকে আপনার কাছে বুদ্ধি-পরামর্শ নিতে আসে।”
“তা বাপু, তোমার কি বিপদ যাচ্ছে?”
হলধর অবাক হয়ে বলে, “তবে আর বলছি কী? বিপদ বলে বিপদ! বিপদের ওপর বিপদ। স্পাই তো লেগেইছে, এখন ভাড়াটে খুনিও এসে গেছে। সাধে কি আর মাঝরাতে উঠে বাঁশবনে এসে লুকিয়ে আছি! মশার কামড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত মশাই, তার ওপর পোকামাকড়েরও তো অভাব নেই।”
নন্দলাল চিন্তিতভাবে বললেন, “একটু খুলে বললে হয় না?”
“সেটাই তো বলার চেষ্টা করছি, আপনিই বাগড়া দিলেন।”
“আচ্ছা আর বাগড়া দেব না, বলে ফেলো।”
“ইংরিজি বইটই কি পড়া আছে ঠাকুরমশাই?”
“না হে বাপু, আমার বংশেই ও চর্চা ছিল না। আমার ঠাকুর্দা বলতেন, ও হল ম্লেচ্ছ ভাষা, শুনলে কানে গঙ্গাজল দিতে হয়।”
“ইংরিজি রূপকথায় ডাইনির গল্প আছে। ডাইনিরা নাকি ঝাটায় চড়ে উড়ে বেড়ায়, জানেন কি?”
“আমার নাতির বইতে ওরকম একটা ছবি দেখেছি বটে!”
“কথাটা হল আমি ছেলেবেলা থেকেই ওই উড়ুক্কু ঝটা নিয়ে খুব ভাবতাম। আমার মনে হল সেই আমলের ডাইনিরা ছিল আসলে বৈজ্ঞানিক, কিন্তু সাধারণ মানুষেরা বিজ্ঞানের কাণ্ড দেখে ভয় পেত বলে বৈজ্ঞানিকদের ডাইনি বলে এড়িয়ে চলত। উড়ুক্কু ঝাটার ছবি তো দেখেছেন তো ঠাকুরমশাই, আমাদের বঁটার মতো নয়। লম্বা একটা লাঠির ডগায় ঝাটাটা লাগানো থাকে।”
“তা দেখেছি বটে।”
“আসলে জিনিসটা হল একটা হালকা পোর্টেবল রকেট, লম্বা ডাণ্ডাটা হল রকেটের বডি আর তলার ঝাটাটা হল আসলে ফুয়েল ডিসচার্জ। রকেট যখন আকাশে ওঠে তখন তলার দিকটায় দেখবেন আগুনের যে হলকা বেরোয় তা অনেকটা বঁটার মতোই দেখায়। আইডিয়াটা মাথায় আসতেই আমার মনে হল, এরকম একটা জিনিস তৈরি করতে পারলে চারদিকে হইচই পড়ে যাবে। এখনকার গাবদা গোবদা রকেটের তো অনেক বায়নাক্কা, যখন-তখন যেখানে-সেখানে ব্যবহার করার জো নেই। কিন্তু উড়ুক্কু ঝাটার মতো হালকা রকেট যেখানে-সেখানে যখন-তখন ব্যবহার করা যাবে। ধরুন বর্ষার জলকাদা ভাঙতে হবে না, খালের ওপর সাঁকোটা ভেঙে পড়লেও চিন্তা নেই, হুড়ুম করে ওপর দিয়ে চলে গেলেন। তারপর ধরুন গিন্নি পুঁইডাঁটা কুটে দেখেন মিষ্টি কুমড়োর জোগাড় নেই। তো চট করে দশ মাইল দূরের ময়নাগড়ের হাট থেকে একফালি কুমড়ো কিনে দশ মিনিটের মধ্যে হাসতে হাসতে চলে এলেন। কিংবা ধরুন আপনার শ্বশুরবাড়ির গাছে খাজা কাঁঠাল পেকেছে, শাশুড়ি খবর পাঠাচ্ছেন, কোনও সমস্যা নেই। উড়ুক্কু ঝাটায় চেপে গিয়ে পেটভরে কাঁঠাল সাঁটিয়ে এলেন।”
নন্দলাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “কাঠালের কথা বলে আর দুঃখ দিও না ভাই। আগে আস্ত একটা কাঁঠাল একাই সাবাড় করতুম। আজকাল আর পেটে সয় না। খেলেই আইঢাই, চোঁয়া ঢেকুর, আমাশা। জিনিসখানা যদি বানাতে পারো তবে যজমানবাড়ি ঘুরে বেড়াতে বড় সুবিধে হয়। এখন চার-পাঁচখানার বেশি লক্ষ্মীপুজো করতে পারি না। ঝটাগাছ হলে দশ বারোখানা হেসে-খেলে পারা যাবে।”
কাঁচুমাচু মুখ করে হলধর বলল, “কাজ তো পনেরো আনা হয়েই গেছে ঠাকুরমশাই, সমস্যা ছিল জ্বালানি নিয়ে। এ রকেট তো হালকা পলকা জিনিস, তেল কয়লা তো আর ভরা যাবে না। তাই বহু খেটেখুটে, মাথা ঘামিয়ে পাঁচ বছরের চেষ্টায় একটা জ্বালানি বানিয়ে ফেলেছি। দিনসাতেক আগেই সেটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি উড়ুক্কু ঝটায় প্রথমে গোঁ গোঁ শব্দ হতে লাগল। তারপর হঠাৎ নড়েচড়েও উঠল। একটু উড়ু উড়ু ভাবও যেন হতে লাগল।”
চোখ বড় বড় করে শুনছিলেন নন্দলাল। সাগ্রহে বললেন, “তারপর? উড়ল নাকি?”
“এই হাতখানেক উঠেছিল, বুঝলুম কাজ প্রায় সেরে এনেছি। জ্বালানিতে আর একটা জিনিস মেশালেই ‘জয় মা দুর্গা’ বলে ঝাটা উড়তে লাগবে।”
“তুমি না নাস্তিক?”
“বটেই তো?”
“এই যে বললে জয় মা দুর্গা?”
“বলেছি নাকি?”
“নির্যস বলেছ!”
“ওটা ধরবেন না, কথার কথা।”
“তুমি পাষণ্ড বটে হে! তারপর ঝাটার কথাটা শেষ করো।”
“আজ্ঞে, পরশুদিনই জ্বালানির কাজও শেষ হয়েছে।” চোখ বড় করে নন্দলাল বললেন, “হয়েছে?”
“হ্যাঁ, তবে প্রয়োগ এবং পরীক্ষা হয়নি। তার আগেই গতকাল সন্ধেবেলা ওই কালান্তক যম এসে হাজির। ঠাকুরমশাই, আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে আমার আয়ু শেষ। কে বা কারা ওই যমদূতকে পাঠিয়েছে তা জানি না। কাল সন্ধেবেলা যখন একমনে কাজ করছি তখন একটা ফোঁস শব্দ পেয়ে পিছন ফিরে দেখি, জানালা দিয়ে ওই দানবটা আমার দিকে জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে রয়েছে। তখনই আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নড়ে উঠল। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। শেষরক্ষা হয় কিনা সেটাই চিন্তার কথা। আমার এতকালের পরিশ্রম, অধ্যবসায় আর সাধনা সবই বুঝি বৃথা গেল।”
নন্দলাল একটু চিন্তা করে বললেন, “লোকটাকে দেখে ভয় লাগারই কথা বটে। কিন্তু সে যে তোমাকেই মারতে এসেছে সেটা
তো এখনও সাব্যস্ত হয়নি।”
“তবে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কথা বলছি কেন?”
“বাপু, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কথা শুনেছি বটে, কিন্তু সেটা কী বস্তু তা জানি না। বলি ষষ্ঠ ইন্দ্ৰিয়টা কী জিনিস বুঝিয়ে বলল তো।”
“সে কি ছাই আমিই জানি। তবে মনে হয় সেটা টিকটিকির মতো একটা কিছু হবে। বিপদ ঘনীভূত দেখলেই সেটা টিক টিক করে ডাকতে থাকে।”
“শোনা যায়?”
“আজ্ঞে না, ঠিক শোনা যায় না। তবে টের পাওয়া যায়।”
“তবে আমার টিকটিকিটা ডাকে না কেন? সেটা কি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?”
“বিপদে পড়লে ঠিকই ডাকবে, কিন্তু ঠাকুরমশাই, আমার এত সাধের আবিষ্কারটার কী হবে? নিশুত রাতে প্রাণের ভয়ে উড়ুক্কু ঝাঁটা আর তার ফর্মুলা নিয়ে পালিয়ে এসে বাঁশবনে গা-ঢাকা দিয়ে আছি। কিন্তু এভাবে তো থাকা যাবে না মশাই।”
“দাঁড়াও বাপু, একটু ভাবতে দাও। বলি পেটে দানাপানি কিছু পড়েছে?”
“আজ্ঞে না। দুশ্চিন্তায় ওসব খেয়ালও করিনি।”
“তবে এই দুটো কলা আর খানকয় বাতাসা রাখো। ঠাকুরের প্রসাদ, ভক্তিতে হোক আর অভক্তিতে তোক একটু কপালে ঠেকিয়ে খেও। এ-বেলাটা বাঁশবনেই ঘাপটি মেরে থাকো, আমি ওবেলা আসবখন।”
নন্দদুলাল খুবই দুশ্চিন্তা নিয়ে বাড়িমুখো হাঁটতে লাগলেন। বিশ কদম যেতে না যেতেই বাধা পড়ল।
“পেন্নাম হই ঠাকুরমশাই।”
“কে রে?”
“এই যে আমি!” নন্দলাল চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে বললেন, “কই হে, কাউকেই যে দেখতে পাচ্ছি না।”
“আজ্ঞে, দয়া করে একটু ঘাড় তুলে ওপরের দিকে তাকাতে হবে যে!”
নন্দলাল ওপরের দিকে চেয়ে দেখলেন, পুরনো আমগাছটার প্রায় মগডালে ভূতনাথ ঘোড়সওয়ার হয়ে বসা।
“বাপু ভূতনাথ!”
“যে আজ্ঞে।”
“এটা কোন ঋতু, তা খেয়াল আছে?”
“ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে এটা তো শরৎকাল বলেই মনে হচ্ছে।”
“তা হলে বাপু, এই শরৎকালে আমগাছে উঠেছ যে বড়? এ তো আমের সময় নয় হে।”
“আজ্ঞে আম নয় ঠাকুরমশাই, খুড়োমশাইয়ের খোঁজে এসেছি।”
“খুড়োমশাই! বলি তোমার খুড়োমশাইয়ের আবার এ-গাঁয়ে কবে আগমন হল? আর এত জায়গা থাকতে বুড়োমানুষ আমগাছেই বা উঠতে গেলেন কেন? পড়ে হাত-পা ভাঙবে যে!”
ভূতনাথ হেসে বলল, “আজ্ঞে সে ভয় নেই। খুড়োমশাইয়ের গাছপালা খুব পছন্দ। হাত-পা ভাঙার উপায় নেই, বায়ভুত জিনিস কি না।”
“হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথায় এসো তো হে।”
“আজ্ঞে। ঠাকুরমশাই, আসল কথাটা বলার জন্যই তো গলা খুসখুস করছে। কিন্তু কাকে বলি বলুন! ভূতনাথের কথা যে কেউ মোটে বিশ্বাসই করতে চায় না। অভয় দেন তো শ্রীচরণে নিবেদন করে ফেলি।”
“তা করে ফেলো বাপু।”
ভূতনাথ গাছ থেকে নেমে এসে ভারী ভক্তিভরে নন্দলালের পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে আর মাথায় ঠেকিয়ে বলল, “আজ্ঞে, কথা তো অনেক। কোনটা আগে বলি, কোনটা পরে সেইটেই সমস্যা। কথার সঙ্গে কথার বড় ঠেলাঠেলি হচ্ছে মশাই, ভেতরে।”
“যেটা আগে বেরোতে চাইছে সেটাকেই বের করে দাও।”
“যে আজ্ঞে। গুরুতর কথাটাই বলি তা হলে। আমাদের হাবু দাসের শরীরে যে আর একটাও হাড়গোড় আস্ত নেই সে-খবর কি শুনেছেন?”
নন্দলাল অবাক হয়ে বললেন, “বলো কী হে? হাবু দাস পালোয়ান মানুষ, তার হাড়গোড় তো সহজে ভাঙার কথা নয়। খাট থেকে ঘুমের ঘোরে পড়েটড়ে গিয়েছিল নাকি?”
ভূতনাথ টপ করে আর একবার খাবলা দিয়ে নন্দলালের পায়ের ধুলো নিয়ে গদগদ হয়ে বলল, “আজ্ঞে, আপনি সিদ্ধপুরুষ, অন্তর্যামী। সবই আগেভাগে জেনে যান। বৃত্তান্তটা অনেকটা তাই বটে। তবে তফাত হল, হাবু পড়ে যায়নি, তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।”
“অ্যাঁ! কার ঘাড়ে দুটো মাথা?”
“আজ্ঞে, উনি বোধ হয় কল্কি অবতারই হবেন। সেইরকমই চেহারাখানা, দেখলে ভক্তিও হয়, ভয়ও হয়।”
“তা হাবুর দোষটা কী?”
ঘাড়টাড় চুলকে ভূতনাথ বলল, “আজ্ঞে, হাবুদাদার মতো মানুষ হয় না, কারও সাতেপাঁচে নেই। চারটি খাওয়া আর ঘুম। কোথা দিয়ে সূর্যোদয় হয়, কোথা দিয়ে অস্ত যায়, তা উনি টেরও পান না। কানে খড়কে দিন, কালীপটকা ফাটান বা কামান দাগুন, হাবুদাদার ঘুম ভাঙার নয়, ওই ঘুমই তো প্রায় কালঘুম হয়ে যাচ্ছিল আর কী!”
“ভণিতা ছেড়ে আসল কথাটায় এলেই তো হয়।”
“আজ্ঞে, পিছনের কথাটা না বললে সামনের কথাটা তেমন পরিষ্কার হয় না কিনা, তা দোষটা ধরুন হাবুদাদারও নয়, দোষ পাঁচুর। কল্কি অবতারটিকে নাকি কর্তাবাবুই এনেছেন। তা পাঁচু বলল, পালোয়ানের ঘরেই পালোয়ন থাকা ভাল। দু’জনে বেশ মানানসই হবে। এই বলে কল্কি অবতারকে তো পাঁচু হাবু দাসের ঘরেই ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু কাঁচাখেগো দেবতাটি বলে বসল, ওই মোটা লোকটা জানালার ধারে ভাল জায়গাটা দখল করে থাকলে তো চলবে না। ওই জায়গাটা আমার চাই। তা পাঁচু মিনমিন করে কী একটু আপত্তি করেছিল যেন। কিন্তু অবতারটি সে-কথায় কান না দিয়ে সোজা হাবু দাসকে নাড়া দিয়ে বলল, ওহে, তোমার বিছানাটা ওই কোণের দিকে নিয়ে যাও, আমি আলো-বাতাস ছাড়া থাকতে পারি না। কিন্তু হাবু দাসের ঘুম ভাঙায় তার সাধ্যি কী! অবতার মানুষ তো, বেশি কথাটথা কইতে জানেন না। এঁরা কাজ ভালবাসেন। বললে বিশ্বাসই করবেন না, তোশকটা ধরে স্রেফ একটা ঝাড়া দিলেন। হাবু দাসের ওই দশাসই বিশমনি শরীরখানা যেন চড়াই পাখিটির মতো উড়ে গিয়ে গদাম করে দশ হাত দূরে পড়ল। কল্কি দেবতার এলেম দেখে আমাদের শরীর হিম হয়ে গেল। পাঁচুর সে কী ঠকঠক করে কাঁপুনি।”
“আ মোলো যা। বলি তাতেও কি হাবুর ঘুম ভাঙেনি! উঠে তো দু-চারটে রদ্দা মারতে পারত।”
“আজ্ঞে। তা হয়তো মারতেনও। কাঁচা ঘুমটা ভেঙেও গিয়েছিল। কিন্তু চোখ মেলেই নিজের হাত-পা খুঁজতে লাগলেন যে! ভারী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কেবল বলছিলেন, ওরে আমার হাত কই? পা কই? এই যে বাঁ হাতটা পেয়েছি, কিন্তু ডান হাতটা কোথায় গেল বল তো! ওরে, আমার মুণ্ডুটা! সেটা তো দেখতে পাচ্ছি না! তা আমরাই সব খুঁজে পেতে দিলাম। হাবুদাদা খুশি হয়ে বললেন, যাক বাবা, সব ঠিকঠাক আছে তা হলে! বেশ, তবে আমি এবার ঘুমোই?”
“এই যে বললে বাপু, হাড়গোড় আর আস্ত নেই?”
“আজ্ঞে, বলেছি। আস্ত নেইও। তবে হাবুদাদার শরীর তো পেল্লায়। অত বড় শরীরের খবর মগজে পৌঁছতে তো একটু সময় লাগবে। না কি? তা ধরুন, দশ মিনিট পরে হাবুদাদা বাপ রে, মা রে’ বলে চেঁচামেচি শুরু করলেন। কোবরেজমশাই এসে বললেন, মোটে সাতখানা হাড় ভেঙেছে।”
“বলো কী হে? এ তো রীতিমত খুনখারাপি!”
“আজ্ঞে। সেই কথাটা বলতে গিয়েই তো গুণেনবাবু কল্কি অবতারের ঠোকাটা খেলেন।”
“এর পর ঠোকনাও আছে নাকি?”
“যে আজ্ঞে। কাল জ্যোৎস্নারাত্তিরে গুণেনবাবুর একটু ভাব এসেছিল। ছাদে উঠে গান গাইছিলেন। গণ্ডগোল শুনে নীচে এসে কাণ্ড দেখে কল্কি অবতারকে গিয়ে একটু তড়পেছিলেন। কী বলব ঠাকুরমশাই, কল্কি অবতার স্রেফ হাই তুলতে তুলতে ছোট্ট করে পিঁপড়ে তাড়ানোর মতো একটা ঠোকনা দিয়েছে কি দেয়নি, অমনি গুণেনবাবু ছিটকে পড়ে চোখ উলটে গোঁ গোঁ করতে লাগলেন।”
নন্দলাল ভারী চটে উঠে বললেন, “গুণ্ডাটা এত কাণ্ড করল আর তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে? কিছু করলে না?”
“আজ্ঞে, করলুম বইকী!”
“কী করলে শুনি?”
“আমরা ওঁর প্রতি ভারী ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করলুম। পাঁচু তো গড় হয়ে পেন্নামই করে ফেললে। ফটিক দু’ টাকা নজরানা অবধি দিয়েছে। আমি যে কী করেছিলুম তা ঠিক স্মরণে নেই বটে, কিন্তু ওরকম ধারাই কিছু একটা হবে।”
“কুলাঙ্গার! কুলাঙ্গার!”
ভূতনাথ খুব আহ্লাদের গলায় বলল, “এখন আপনি কুলাঙ্গার বলায় একটু লজ্জা-লজ্জা করছে বটে, কিন্তু গতকাল কুলাঙ্গার হতে পেরে কিন্তু ভারী আনন্দ হয়েছিল ঠাকুরমশাই।”
“বটে!”
“যে আজ্ঞে। তবে কল্কি অবতার আমাকেও ভারী বিপদে ফেলেছেন ঠাকুরমশাই। কালকের ওই হুলুস্থুলু দেখে খুড়োমশাই ভড়কে গিয়ে তফাত হয়েছেন। তাঁর আর টিকির নাগালটিও পাচ্ছি না। একটা গুপ্তধনের হদিস দেবেন বলে ক’দিন হল ঝুলিয়ে রেখেছেন। এখন তাঁর সন্ধান না পেলে যে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে আমার।”
“খুড়োমশাইটি কে বলো তো!”
“আজ্ঞে, তিনি হলেন কর্তাবাবুর ঊর্ধ্বতন তৃতীয় পুরুষের খাজাঞ্চি। পঞ্চাশ বছর হল গত হয়েছেন। আমাকে বড্ড স্নেহ করেন।”
“অ। তোমার যে আবার ভূতের কারবার তা তো ভুলেই গিয়েছিলুম বাপু।”
ভারী বিনয়ের সঙ্গে ভূতনাথ বলল, “আমার আর কী কারবার দেখছেন ঠাকুরমশাই। মাঠ গোবিন্দপুরের নিবারণ গড়াইয়ের কারবার তো দেখেননি! অশৈলী কাণ্ডকারখানা।”
“সে কি ভূতের পাইকার নাকি?”
“তা বলতে পারেন। তার ভূতের আড়ত দেখলে ভিরমি খাবেন। বিশ-পঁচিশজন কর্মচারী কারবার সামলায়।”
২. হাবু দাসের মাথাটি ভারী পরিষ্কার
রাত থেকেই হাবু দাসের মাথাটি ভারী পরিষ্কার লাগছে। একদম ঝকঝকে পরিষ্কার। কোথাও কোনও দাগ বা আঁচড় অবধি নেই। এই যেমন সে একটা ঘরে একটা বিছানায় শুয়ে আছে, কিন্তু এটা কার ঘর, কার বিছানা এসব কিছুই তার মনে পড়ছে না। এমনকী এটা কোন জায়গা, তার নিজের নামটাই বা কী, বা তার বাবার নামই বা কী ছিল এ সবই মাথা থেকে বেমালুম মুছে গেছে। তাতে অবশ্য হাবুর বেশ আনন্দই হচ্ছে। তার সারা শরীরে কে বা কারা যেন নানারকম পট্টি, পুলটিশ আর ব্যান্ডেজ লাগিয়েছে। সেটাও হাবুর খুব একটা খারাপ লাগছে না। ব্যাপারটা সাজগোজ বলেই মনে হচ্ছে তার। হাত পা মাথা ব্যথায় যে টনটন করছে সেটাও তেমন অপছন্দ করতে পারছে না হাবু। টনটন না করা কি ভাল? হাত পা আছে অথচ টনটন করছে না, সেটা তো ভাল কথা নয়! টনটন না করলে হাত পা যে আছে তা বোঝাই বা যাবে কী করে? তাই হাবুর বেশ ফুর্তিই হচ্ছিল। ফুর্তির চোটে রাতে ঘুমই হল না মোটে।
সকালে খুব আহ্লাদের সঙ্গে বিছানায় বসে ছিল হাবু। আলো ফুটেছে, পাখি ডাকছে, চারদিকে একটা হাসিখুশি ভাব। জায়গাটা ভারী নতুননতুন লাগছে। নিজেকেও ভারী নতুন লাগছে তার। তবে নামটা মনে পড়ছে না। তাতে অবশ্য ভালই হয়েছে। নতুন একটা নাম ঠিক করে নিলেই হবে।
নিজের কী নাম রাখা যায় তা খুব ভাবতে লাগল হাবু। আচ্ছা, সকাল সরকার নামটা কেমন? মন্দ নয়, তবে কোকিল কাহার নামটা কি আরও একটু ভাল? আচ্ছা, জানালা পাল কি খুব খারাপ নাম? কিংবা ভোরের আলো সেন? পাশের আতাগাছে বসে একটা কাক খুব ডাকাডাকি করছে। কানখাড়া করে শুনে খুশি হল হাবু, হ্যাঁ বায়স বসু নামটাও তো খারাপ শোনাচ্ছে না!
এমন সময় দরজা ঠেলে একটা লোক ঘরে ঢুকল। বেশ লোক। পরনে হেটো ধুতি, গায়ে ফতুয়া, কাঁধে গামছা, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।
হাবু লোকটাকে ডেকে বলল, “ওহে বাপু, বলল তো কোন নামটা আমাকে মানাবে! বেশ ভেবেচিন্তে বোলো কিন্তু। সকাল সরকার, কোকিল কাহার, জানালা পাল, ভোরের আলো সেন, বায়স বসু।”
লোকটা অবাক হয়ে বলে, “সে কী গো হাবুদাদা, পিতৃদত্ত নামটা থাকতে আবার নতুন নাম রাখতে যাবে কেন? হাবু নামটা তো খারাপ নয়। দিব্যি নাম।”
হাবু নাক সিঁটকে বলল, “এঃ, আমার নাম হাবু নাকি?”
“তবে! এ নামেই তো সবাই তোমাকে চেনে!” হাবু ভাবল, এ লোকটা বোধ হয় অনেক খবর রাখে, এর কাছ থেকেই কায়দা করে সব জেনে নিতে হবে।
হাবু চোখ কুঁচকে বলল, “আচ্ছা, আমার নাম যদি হাবু হয়, তা হলে তোমার নামটা কী হবে?”
লোকটা ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে বলল, “কাল কদম ওস্তাদের অমন আছাড়টা খেয়েও তোমার মশকরা করতে ইচ্ছে যাচ্ছে? ধন্যি মানুষ বটে তুমি? কাল অমন কুরুক্ষেত্তর হল, তায় সারারাত আমাদের কারও চোখে ঘুম নেই। ওই কালাপাহাড় বিভীষণ এখন কাকে ধরে, কাকে খায় সেই চিন্তাতেই ভয়ে মরছি।
এ সময়ে কি মশকরা ভাল লাগে গো হাবুদাদা?”
হাবু খিকখিক করে হেসে বলল, “পারলে না তো!”
“কী পারলুম না?”
“বলতে পারলে না তো যে, আমার নাম যদি হাবু হয় তা হলে তোমার নাম কী হবে? বলতে পারলে বুঝব তুমি বাহাদুর বটে।”
“আর বাহাদুর হয়ে কাজ নেই বাপু। যা কাল দেখলুম তাতে বাপের নাম ভুলে যাওয়ার জোগাড় তো নিজের নাম।”
হাবু মিটমিট করে চেয়ে বলল, “ভুলে গেছ তো! তা হলে বাপু, ভাল দেখে নিজের একটা নাম রাখলেই তো হয়। আচ্ছা, পাঁচকড়ি নামটা কেমন বলো তো!”
লোকটা ভারী করুণ মুখ করে বলল, “আহা, কতকাল ও নামে কেউ ডাকেনি আমাকে! পিতৃদত্ত নাম, কিন্তু তার ব্যবহারই হয় না। সবাই ‘পাঁচু পাঁচু’ বলে ডেকে ডেকে ও নামটা বিস্মরণই করিয়ে দিয়েছে। তাও ভাল, নামটা মনে করিয়ে দিলে। কিন্তু তুমি জানলে
কী করে বলো তো! এ নাম তো কারও জানার কথা নয়।”
হাবু খুব খিকখিক করে হাসতে লাগল। বলল, “আচ্ছা, এবার তোমাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি। খুব ভেবেচিন্তে বলবে কিন্তু! আচ্ছা, বলো তো, আমার নাম হাবু আর তোমার নাম পাঁচু হলে এ বাড়িটা কার?”
পাঁচু হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল, “এ আবার কোনদিশি ধাঁধা গো হাবুদাদা? এ হল কর্তাবাবুদের সাতপুরুষের ভিটে। বাচ্চা ছেলেও জানে। রাঘব চৌধুরীর বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করলে রাস্তার গোরুটাও পথ দেখিয়ে দেবে।”
হাবু হাততালি দিয়ে বলল, “বাঃ, এই তো পেরেছ। এবার একটা খুব শক্ত ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি কিন্তু। ঘাবড়ে যেও না, মাথা ঠাণ্ডা রেখে জবাব দিও। আচ্ছা বলো তো আমার নাম হাবু, তোমার নাম
পাঁচু আর বাড়িটা রাঘববাবুর হলে এ গাঁয়ের নামটা কী?”
“বলি, তোমার মাথাটাই গেছে নাকি? গত দেড় বছর ধরে তো হাট গোবিন্দপুরে থানা গেড়ে আছে, রাতারাতি কি গাঁয়ের নাম পালটে যাবে?”
একগাল হেসে হাবু বলল, “না হে, তোমাকে মেডেল দেওয়া উচিত। তুমি তো দেখছি ধাঁধার ধন্বন্তরি!”
“এখন রসিকতা রেখে খাবারটা খেয়ে নাও। রোজ তোমার বরাদ্দ সকালে কুড়িখানা রুটি। আজ মোটে পনেরোখানার বেশি হল না, ওই যক্ষটাই তো সকালে সত্তরখানা রুটি সাবাড় করল। আমরা ভয়ে কেউ রাটি কাড়িনি।”
কিন্তু খাবারের কথা শুনেও মোটেই চঞ্চল হল না হাবু। খাবে কী, আজ তার এত ফুর্তি হচ্ছে যে, ফুর্তির চোটে খিদেই উধাও। পাঁচু চলে যাওয়ার পর সে উঠে পড়ল। মাজায় ব্যথা, ঘাড় টনটন, হাত পা ঝনঝন, তবু হাবুর গ্রাহ্য নেই। এই নতুন জায়গাটা ভাল করে চিনে নিতে হবে। লোকজনের সঙ্গেও আলাপ সংলাপ করতে হবে। ভাব-ভালবাসা করাটা খুবই দরকার। তার যে বড়ই আনন্দ হচ্ছে।
বাইরে বেরিয়েই সামনে একজন লোককে পেয়ে তাকে একেবারে বুকে টেনে নিয়ে হাবু বলল, “এই যে ভায়া, কতকাল পরে দেখা! আচ্ছা, একটা ভারী মজার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে? খুব হুঁশিয়ার হয়ে দেবে কিন্তু। ভুল হলেই নম্বর কাটা যাবে। আচ্ছা, বলো তো, আমার নাম যদি হাবু হয়, পাঁচুর নাম যদি হয় পাঁচু, আর এটা যদি রাঘববাবুর বাড়ি হয় আর গাঁয়ের নাম যদি হয় হাট গোবিন্দপুর, তাহলে তোমার নামটা কী হবে! বেশ শক্ত প্রশ্ন কিন্তু।”
লোকটা খুব গম্ভীর হয়ে কর গুনে গুনে অনেকক্ষণ ধরে হিসেব করল। একবার যেন তোর ঘরের নামতাও বলল। এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের কথাও বিড় বিড় করে নিল। একবার মাথা ঝাঁকাল, দুবার ঘাড় চুলকে তারপর হঠাৎ উজ্জ্বল মুখে বলল, “হয়েছে! তোমার নাম হাবু, পাঁচুর নাম পাঁচু, এটা রাঘববাবুর বাড়ি আর গায়ের নাম হাট গোবিন্দপুর হলে আমার নামটা দাঁড়াচ্ছে গোলাপ রায়।”
“বাঃ বাঃ! দশে তোমাকে দশ দিলুম। বুঝলে! দশে দশ।”
গুণেন জানত, একদিন তার গলায় সুর খেলবেই। তার ভিতরে সুরের বারুদ একেবারে ঠাসা। শুধু একটা ফুলিঙ্গের অপেক্ষা ছিল। ওই স্ফুলিঙ্গের অভাবেই তার গলার কামানটা কিছুতেই গর্জে উঠতে পারছিল না। গান সে গাইত বটে, কিন্তু ভিতরে যে সুরের ঠাসাঠাসি তা বেরিয়ে আসতে পারল কই? এই নিয়ে ভারী দুঃখ ছিল গুণেনের কিন্তু বিশ্বাস ছিল একদিন ভগবানের আশীর্বাদ ঠিকই নেমে আসবে তার ওপর। তখন সুরসপ্তক বেরিয়ে এসে চারদিক কাঁপিয়ে দেবে।
কখন যে কার ভাগ্য খোলে তার কিছু ঠিক নেই। ভগবানকে দোষ দিয়ে তো লাভ নেই। তাঁর পাঁচটা কাজ আছে। ব্যস্ত মানুষ। একটা সেরে তবে তো আর একটায় হাত দেবেন! তাই আশায় আশায় অপেক্ষা করছিল গুণেন। কবে ভগবানের হাত খালি হয়, কবে তিনি গুণেনের দিকে তাকান।
গতকাল সন্ধেবেলাতেই ভগবান তাঁর দিকে তাকালেন। আর সে কী তাকানো বাপ রে! রক্ত জল হয়ে যায়। তাঁর আশীর্বাদটাও নামল একেবারে বজ্রের মতো। ঠিক বটে আশীর্বাদের ধরনটা তখন ঠিক পছন্দ হয়নি গুণেনের। কিন্তু পৃথিবীর উপকারী জিনিসগুলোর বেশির ভাগেরই স্বাদ মোটেই ভাল হয় না। এই যেমন নিমপাতা, গ্যাঁদাল, উচ্ছে, হিঞ্চে, কাঁচকলা, কবিরাজি পাঁচন কি কুইনাইন কিংবা ইনজেকশন। তাই আশীর্বাদটা যখন গুণেনের ওপর এসে পড়ল তখন গুণেনও ওটা আশীর্বাদ বলে বুঝতেই পারেনি। পাছে আর পাঁচজনে টের পায় এবং তাদের চোখ টাটায়, সেইজন্যই বোধ হয় ভগবান আশীর্বাদটাকে একটা ঠোকনার মতো করে দিলেন।
কাল জ্যোৎস্না রাত্তির ছিল। সন্ধেবেলা ছাদে উঠে গুণেন গুগুন করে খানিকক্ষণ গলাটলা খেলিয়ে একটা চেঁচামেচি আর ধুপধাপ শব্দ শুনে নীচে নেমে এসে দেখে, হাবু পালোয়ানের ঘরে দক্ষযজ্ঞ হচ্ছে। হাবু মেঝের ওপর চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে, লোকজন সব কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা আর অন্যধারে স্বয়ং শিব দাঁড়িয়ে। সত্যি কথা বলতে কী, শিবের সঙ্গে এঁর কিছু কিছু তফাত ছিল। যেমন জটা ছিল না, বাঘছাল ছিল না, মাথায় সাপ ছিল না, গায়ে ভস্ম মাখা ছিল না। দেবতারা তো আর স্বমূর্তিতে দেখা দেন না। তাই গুণেনও চিনতে পারেনি। উটকো একটা লোক এসে ঝামেলা পাকাচ্ছে মনে করে সে তেড়ে গিয়ে লোকটাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, “কে হে তুমি, গুণ্ডামি করতে এসেছ? এ তো তোমার ভারী অন্যায় হে?”
তখনই আশীর্বাদটা এল। একটা ঠোকর ছদ্মবেশেই এল। এসে লাগল গুণেনের চোয়ালে। তারপর কিছুক্ষণ আর গুণেনের জ্ঞান ছিল না। যখন জ্ঞান ফিরল তখন সে নিজের ঘরে, বিছানায় শুয়ে আছে। চোয়াল আর মাথা ছিঁড়ে পড়ছে ব্যথায়।
ব্যাপারটা যে আশীর্বাদ, তা তখনও বুঝতে পারেনি বটে। বুঝল একটু রাতের দিকে। যতবার ব্যথায় ককিয়ে উঠছে, ততবারই মনে হচ্ছে তার আর্তনাদেও যেন সুর লেগে যাচ্ছে। কখনও পূরবীতে “বাবা গো, মা গো” করে উঠছে, কখনও মালকোষ লেগে যাচ্ছে “মরে গেলুম রে, আর রক্ষে নেই রে” চেঁচানিতে। শেষে যখন “ওরে, তোরা কোথায়, আমাকে ধরে তোল” বলে চেঁচাতে গিয়ে গলায় বেহাগ লেগে গেল, তখন আর থাকতে না পেরে গুণেন উঠে পড়ল। তাই তো! গলায় এত সুর আসছে কোথা থেকে? তবে কি বারুদে আগুন লেগেছে? ঘুমন্ত কামান কি জাগল?
তানপুরাটা নামিয়ে বসে গেল গুণেন। দরবারি কানাড়া। আহা, সুর যেন রাধধনু ছড়াতে ছড়াতে বেরিয়ে আসতে লাগল। কী গলা, কী গিটকিরি! কুকুরগুলো অবধি ঘেউ ঘেউ না করে জানালার বাইরে বসে ল্যাজ নেড়ে নেড়ে শুনতে লাগল। তারপর মালকোষ। সুরের মায়াজালে যেন প্রকৃতির চোখে জল ঝরতে লাগল শিশিরবিন্দু হয়ে। নিজের গলাকে মোটেই চিনতে পারছিল না গুণেন। ভোরের দিকে সে ধরল আহির ভৈরোঁ। ধরামাত্রই গোয়াল থেকে রাঘববাবুর বারোটা গোরু একসঙ্গে জেগে উঠে গম্ভীর নিনাদে তাকে অভিনন্দন জানাল। আর সুরের ঠেলায় শিউলিফুল ছিটকে ছিটকে পড়তে লাগল ঘাসে। আর সূর্যদেব থাকতে না পেরে দশ মিনিট আগে উদয় হয়ে পড়লেন।
রাগরাগিণী ঠিকমতো গাইতে পারলে নানারকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়, প্রদীপের সলতে জ্বলে ওঠে, মেঘ করে বৃষ্টি হয়, আরও কত কী শুনেছে গুণেন।
তানপুরাটা রেখে গুণেন প্রথমে চোখের আনন্দাশ্রু মুছল। তারপর চারদিক চেয়ে ভারী অবাক হয়ে দেখল, মেঝেতে একটা টিকটিকি আর তার পাশে দুটো মাকড়সা মরে পড়ে আছে। আরও একটু খুঁজতেই দেখল শুদ্ধ সুরের হস্কায় পাঁচ-পাঁচটা আরশোলাও অক্কা পেয়েছে। আসল গান যে কী জিনিস তা আজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারল গুণেন।
কিন্তু সুর দিয়ে প্রাণী-হত্যা করাটা কি ঠিক? এই ভেবে মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল তার।
বাইরে কোকিল ডাকছে না? হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। এই শরৎকালে তো কোকিলের ডাকার কথাই নয়! তবে কি সুরের খোঁচা খেয়ে ওদের গলাতেও গান এসে গেল!
সে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে কান খাড়া করে কোকিলের ডাক শুনল। সামনেই পরাণ মালি বাগানের মাটি কোপাচ্ছে।
গুণেন গিয়ে তাকে বলল, “পরাণভাই, কোকিল ডাকছে কেন বলো তো!”
পরাণ নির্বিকার মুখে বলল, “এখানে সব বারোমেসে কোকিল মশাই, যখন-তখন ডাকে।”
কথাটা মোটেই সত্যি নয়। কোকিল কোথাও বারোমাস ডাকে না, বারোমেসে কোকিল বলেও কিছু নেই। কিন্তু এ নিয়ে পরাণ মালির
সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। ওরা একটা বুঝতে আর-একটা বোঝে।
তবু হাসি-হাসি মুখ করে সে পরাণকে জিজ্ঞেস করল, “গান শুনলে বুঝি? শরীরটা বেশ তরতাজা, ঝরঝরে লাগছে না?”
পরাণ অবাক হয়ে বলল, “গান! গান হচ্ছিল নাকি? কই, গান শুনেছি বলে তো মনে হচ্ছে না! একটা চেঁচানি শুনছিলুম বটে। ওই চেঁচানির ঠেলায় গান আর কানে এসে পৌঁছয়নি।”
একটু দমে গেল গুণেন। গানটা চেঁচিয়েই গাইতে হয় বটে, কিন্তু সেটাকে চেঁচানি বলাটা কি একটু বাড়াবাড়ি নয়? তা যাকগে, সমঝদার ছাড়া এ জিনিস তো আর কেউ বুঝবে না।
গোয়ালঘরের উঠোনে গেনু গয়লা দুধ দোয়াচ্ছিল। গুণেন শুনেছে, ভাল গান শোনালে গোরু নাকি বেশি দুধ দেয়। সে গিয়ে কিছুক্ষণ দুধ দোয়ানো দেখল। তারপর মুরুব্বির মতো জিজ্ঞেস
করল, “ওরে গেনু, দুধটা যেন একটু বেশি বেশি মনে হচ্ছে।”
“হাঁ হাঁ, কাহে নেহি? গোরুকে ঠিকমতো দেখভাল করলে জেয়াদা দুধ কাহে নাহি দিবে? হামি রোজ গোরুকে ঘাস বিচালি, লালি গুড়, খইল খিলাচ্ছি, উসি লিয়ে তো দুধ ভি জেয়াদা দিচ্ছে।”
“ওরে না। সে কথা নয়। সেসব তো রোজই খায়। তবু যেন আজ দুধটা একটু বেশিই দিয়ে ফেলছে!”
“কিউ নেহি বাবু? মুলতানি গাই আছে, যত খিলাবেন তত দুধ বাড়িয়ে যাবে। কাল রাঘববাবু তো ইসকো দো সের রসগুল্লা ভি খাইয়েছেন। উসি লিয়ে দুধ জেয়াদা দিচ্ছে।”
কথাটা মোটেই মনঃপূত হল না গুণেনের। ও ব্যাটা আসল ব্যাপারটা বুঝতেই পারেনি। কিন্তু গুণেন গোরুটাকে ভাল করে লক্ষ করে দেখল, মুখটা বেশ হাসি-হাসি। আর চোখে কেমন একটা বিভোর ভাব। অবোলা জীব, কথা তো আর কইতে পারে না, কিন্তু গুণমুগ্ধ চোখে গুণেনের দিকে চেয়ে আছে।
“হ্যাঁ রে গেনু, তুই গানবাজনা ভালবাসিস?”
“হাঁ হাঁ, জরুর। গান বাজনা তো হামার বহুত পসন্দ আছে। রোজ রাতে তো আমি ঢোল বাজাই আর রামা হো, রামা হো গানা ভি গাই।”
“ও গান নয় রে। এই যে একটু আগে আমি আলাহিয়া বিলাওল গাইলাম, শুনিসনি?”
“কাহে নেহি শুনবে বাবু? জরুর শুনেছে। উ তো বহুৎ উমদা গানা আছে বাবুজী। শুনে আমার দাদিমার কথা ইয়াদ হল।”
“কেন রে, তোর দিদিমার কথা মনে পড়ল কেন? তোর দিদিমা গান গাইত বুঝি?”
“নেহি বাবু, দাদিমা থোড়াই গান গাইবে। লেকিন হামার দাদিমা রোতা থা। কুছু হলেই দাদিমা কাঁদতে বইসে যেত। গরম পড়লে কাঁদত, শীত পড়লে কাঁদত, বরখ হলে কাঁদত। কাক বক মরলে কাঁদত। এইসন কাঁদত যে আশপাশ গাঁওমে কোই মারাটারা গেলে দাদিমাকে ভাড়া করে কাঁদবার জন্য নিয়ে যেত। আপনার গান শুনে হামার খুব দাদিমার কথা ইয়াদ হচ্ছে।”
ধুস! ব্যাটা গানের কিছুই বোঝে না। সমঝদার না হলে এইসব উচ্চাঙ্গের জিনিস বুঝবেই বা কে?
তবে খানিকটা দমে গেলেও আশার আলোও যে দেখা গেল না তা নয়। বুড়ো খাজাঞ্চি খগেন দফাদার তো গুণেনকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, “আহা, কী গানই না গাইলে হে গুণেন! কোনওকালে আমি কালোয়াতি গান পছন্দ করিনি। বরাবর মনে হয়েছে ও হল গলাবাজি করে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা। তা বাপু, তোমার গান শুনে দেখলুম এ গান খুবই উপকারী জিনিস।”
গুণেন সোৎসাহে বলল, “বটে! তা কী হল খাজাঞ্চিমশাই!”
“কাল পুকুরে চান করতে গিয়ে ডান কানে জল ঢুকে গিয়েছিল। কিছুতেই বেরোয় না। সারাদিন কান টনটন করেছে। খড়কে দিয়ে খুঁচিয়ে, তুলোর ঢিপলি ঠেসেও জল বের করা যায়নি। তারপর রাত্তিরে তোমার গান শুনে কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে বসে যখন তোমাকে শাপ শাপান্ত করছি, তখনই অবাক কাণ্ড হে! গানের ধাক্কায় কানের জল সুড়সুড় করে বেরিয়ে এল। সে যে কী আরাম, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। চালিয়ে যাও হে, তোমার হবে।”
আনন্দে ডগমগ হয়ে গুণেন তার গানের আর কী কী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হল তা দেখতে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল।
“এই যে ভাইটি!”
সামনে পর্বতপ্রমাণ হাবুদাসকে দেখে গুণেন হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়াল। হাবু দাসের চোখমুখে ভাবের খেলা দেখেই সে বুঝেছে গানের সম্মোহনে হাবু সমাচ্ছন্ন।
হাবু দাস ফিচিক করে হেসে বলল, “তোমাকে একটা মজার ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি। ভেবেচিন্তে বলো তো দেখি। এই আমার নাম যদি হাবু হয়, পাঁচুর নাম যদি হয় পাঁচু, গোলাপ রায়ের নাম যদি হয় গোলাপ রায়, এবাড়িটা যদি রাঘববাবুর হয়, আর এ গাঁয়ের নাম যদি হয় হাট গোবিন্দপুর, তা হলে তোমার নামটা কী হবে?”
“অ্যাঁ।”
“হ্যাঁ, খুব সোজা অঙ্ক। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করলেই বেরিয়ে পড়বে। তাড়া নেই, ভেবেচিন্তে বলল তো!”
গুণেন হাঁ হয়ে গেল। বলল, “তার মানে?” খিকখিক করে হেসে হাবু বলল, “পারলে না তো! দুয়ো, দুয়ো।”
বলেই হনহন করে হেঁটে চলে গেল। তার গানের প্রভাবে যে চারদিকে নানারকমের পরিবর্তন হয়েছে সে বিষয়ে গুণেনের সন্দেহ রইল না। কিন্তু দুনিয়াটা এতটা বদলে যাওয়া কি ভাল?
গুণেন হঠাৎ থমকে গেল। তাই তো! হাবু তো কিছু ভুল বলেনি। বাস্তবিক হঠাৎ এখন খেয়াল হল, নিজের নামটা তো সত্যিই মনে পড়ছে না! কী যেন নামটা তার!
৩. রাঘববাবুর বাঁ কান কাঁপলে
রাঘববাবুর বাঁ কান কাঁপলেই বুঝতে হবে বিপদ আসছে। তেরো বছর আগে যখন প্রথমবার তাঁর বাঁ কান কেঁপেছিল সেবারই শ্বশুরবাড়িতে কাঁঠাল খেয়ে তাঁর কলেরা হয়। বছর দুই বাদে ফের একদিন বাঁ কান কেঁপে উঠেছিল, আর সেবারই হিমে ডাকাত হানা দিয়ে তাঁর টাকাপয়সা সোনাদানা সব চেঁছেছে নিয়ে তো যায়ই, উপরন্তু রাঘববাবুর খুড়োমশাই অবসরপ্রাপ্ত দেশনেতা মাধব চৌধুরী ডাকাতির সময় ডাকাতদের উদ্দেশ্যে দেশের নৈতিক অধঃপতন বিষয়ে একটা সময়োচিত নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন বলে তাঁর পেটে একটা বল্লমের খোঁচাও মেরে যায়। সেই খোঁচা থেকেই কিনা কে জানে, খুড়োমশাই বাকি জীবন অম্লশূলে ভুগেছেন। এই ঘটনার চার বছর বাদে ফের এক সকালে রাঘববাবুর বাঁ কান নেচে উঠল এবং সেবার বাড়ির উঠোনে ‘নদের নিমাই’ যাত্রার আসরে ঝাড়বাতি ভেঙে পড়ে শচীমাতার নাক ফেটে গিয়েছিল বলে তিনি মামলা করে রাঘববাবুর কাছ থেকে মোটা খেসারত আদায় করেছিলেন। কারণ নাক ফেটে যাওয়ায় তিনি নাকি আর নাকিসুরে বিলাপ করতে পারতেন না এবং নাকিসুরের বিলাপ ছাড়া শচীমাতার পার্টে আর থাকেটা কী? এই তো বছরতিনেক আগে ফের ঘুমন্ত বাঁ কান হঠাৎ জেগে উঠেনড়াচড়া করে উঠল। সেবার বেয়াই রামশরণ সমাদ্দারের সঙ্গে দাবা খেলার সময় একটা কাঠপিঁপড়ে কামড়ে দেওয়ায় আত্মবিস্মৃত হয়ে রাঘববাবু ভুল করে মন্ত্রীকে আড়াই ঘরের চালে চেলে ফেলেছিলেন। এবং তাতে রামশরণের একটা বিপদজ্জনক গজ মারা পড়ে। রামশরণ সেটা বুঝতেও পারেননি। কিন্তু তাঁর ফাজিল ভাগ্নে ফটিক ভারী নিরীহ গলায় বলেছিল, তালুইমশাইয়ের চালটা দেখলে মামা? মন্ত্রীকে যে ঘোড়ার চালেও চালানো যায় ক’টা লোকই বা তা জানে! ওঁর কাছে অনেক কিছু শেখার আছে কিন্তু। কথাটা শুনে রামশরণ সচকিত হয়ে চালটা দেখে রেগে কাঁই হয়ে জলগ্রহণ না করে রাঘববাবুর বাড়ি থেকে সেই যে চলে গেলেন আজ অবধি আর এ-মুখো হননি। বউমাকে পর্যন্ত বাপের বাড়িতে আসতে দেননি।
তাই আজ সকালবেলায় দুর্গানাম করার সময় যখন টিকটিকি ডেকে উঠল, দুধের বাটিতে মাছি পড়ল এবং মনের ভুলে যখন উলটো গেঞ্জি পরে ফেললেন, তখনও রাঘববাবু ঘাবড়াননি। তার পরে যে ঘটনাটা ঘটল, সেটাই মারাত্মক। এ বাড়িতে প্রায়ই একটা গুণ্ডা এবং হিংস্র হুলো বেড়াল হানা দেয়। কেঁদো বাঘের মতো ডোরাকাটা চেহারা, আকারে চিতাবাঘের কাছাকাছি। সে কাউকেই বড় একটা পরোয়া করে না। কিন্তু বাড়ির মালিক রাঘববাবুর প্রতি তার তাচ্ছিল্য আরও বেশি। রাঘববাবু তাকে বহুবার ঠ্যাঙা নিয়ে তাড়া করেছেন। কিন্তু হুলোর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেননি। বরং হুলো একটু নিরাপদ দূরত্বে থেকে নিজের ভাষায় রাঘববাবুকে নানারকম ব্যঙ্গবিদ্রূপও করে থাকে। আজও হুলো যথারীতি তার নানারকম চোরা পথে বাড়িতে ঢুকেছে এবং ঝি মোক্ষদাকে বিকট মুখভঙ্গি করে ভয় দেখিয়ে প্রায় তার হাত থেকেই প্রকাণ্ড দুটো কই মাছ ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছিল। হইহই শুনে রাঘববাবু যথারীতি ঠ্যাঙা নিয়ে হুলোকে তাড়া করলেন। কিন্তু আজকের দিনটা হুলোর ছিল না। বুদ্ধিভ্রংশ না হলে সে চোরকুঠুরিতে ঢুকতে যাবেই বা কেন? একটামাত্র দরজা ছাড়া চোরকুঠুরি থেকে বেরনোর পথ নেই। হুলো সেই কুঠুরিতে ঢুকতেই রাঘববাবু তার পিছু পিছু ঢুকে দরজা সেঁটে দিয়েছিলেন। খুব ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল হুলো। রাঘববাবু তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঠ্যাঙা আস্ফালন করে একটু হেসে বললেন, “এবার তোর কী হবে রে হুলো! ঘুঘু দেখেছিস, ফাঁদ দেখিসনি তো! এবার তোর জারিজুরি শেষ। ইষ্টনাম জপ রে ব্যাটা, ইষ্টনাম জপ।”
হুলো তার নিজস্ব ভাষায় যা বলল তা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, “কেন কর্তাবাবু, মিছিমিছি ঝামেলা করছেন? বেড়াল বলে কি আর মানুষ নই মশাই! ওই যে কতগুলো অপোগণ্ড নিষ্কর্মা দু’ পেয়ে জীবকে পুষছেন, কই তাদের তো কিছু বলেন না! আমি তো তবু খেটে খাই। একটা মাছ কি একটু দুধ জোগাড় করতে কত মেহনত বলুন তো, প্রাণের ঝুঁকিও কি কম? এবারটা না হয় মাফ করে দিন।”
কথাগুলো যে রাঘববাবু একেবারেই বুঝতে পারলেন না, তা নয়। কিন্তু বুঝেও তিনি অবিচল গলায় বললেন, “তা হয় না হুলো, লোকে আমাকে কাপুরুষ বলবে।”
‘মরতে যদি হয় তবে আমি বীরের মতোই মরব কর্তামশাই। তবে মরার আগে আপনাকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বেড়াল হল মা-ষষ্ঠীর বাহন। বেড়াল মারা মহাপাপ। মারলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তার অনেক খরচ এবং ঝামেলা।”
বজ্রগম্ভীর স্বরে রাঘববাবু বললেন, “আমি কুসংস্কারে বিশ্বাসী নই রে হুলো। ওসব বলে আমাকে ভড়কে দিতে পারবি না।”
“ভাল করে ভেবে দেখুন কর্তামশাই, মাত্র দুটো কইমাছের জন্য আপনি নরকের পথ পরিষ্কার করবেন কিনা। দুটো কইমাছের দাম মাত্র দেড় টাকা। এই সামান্য টাকার জন্য মহাপাতকী হওয়া কি ভাল? মাত্র দেড় টাকায় নরকের টিকিট?”
রাঘববাবু হুঙ্কার দিয়ে বললেন, “কে বলেছে দেড় টাকা? তুই কি সত্যযুগে আছিস নাকি রে হুলো? আমার হিসেবমতো ও দুটো কই মাছের দাম সাড়ে ছয় টাকার নীচে নয়।”
“কর্তামশাই, এখন জো পেয়ে যা খুশি বললেই তো হবে না। ঠিক আছে, আপনিও একটু নামুন, আমিও একটু উঠি। মাঝামাঝি একটা রফা হয়ে যাক।”
“কত?”
“সাড়ে তিনা।”
“না, সাড়ে চার।”
“তা হলে চারই থাক। আর চাপাচাপি করবেন না। এখন ভেবে দেখুন বছরে যার হেসেখেলে পাঁচ-সাত লাখ টাকা আয়, যার গোয়ালে আটটা দুধেল গাই, বছরে দেড়শো মন ধান, তেজারতির রোজগারের লেখাজোখা নেই, সেই মানুষের কাছে চারটে টাকা কোনও টাকা হল কর্তামশাই? চার টাকায় যে এক পো ডালও হয় না!”
হাঃ হাঃ করে হেসে রাঘববাবু বললেন, “তুই আমাকে বাজার দর শেখাচ্ছিস নাকি রে হুলো? বাজারে আমি নিজে যাই না বটে, কিন্তু দরদাম সব আমার মুখস্থ।”
“কিছু মনে করবেন না কর্তাবাবু, ভাববেন হয়তো কুচ্ছো গাইছি, কিন্তু আপনার বাজার সরকার খগেন দফাদার কিন্তু বাজারের পয়সা থেকে চুরি করে। আর শুধু খগেনই বা কেন, ওই যে আপনার পেয়ারের চাকর পাঁচু, সে তো প্রায় রোজই দুপুরে আপনার গড়গড়ায় চুরি করে তামাক খায়। নবকৃষ্ণ পাটাতনের জঞ্জাল সাফ করতে গিয়ে তিন-তিনটে মোহর পেয়েছিল, সেগুলো কি আপনাকে দিয়েছে? ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে, তবু অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসছে বলেই সাহস করে বলে যাই। স্বয়ং গিন্নিমা তারাসুন্দরী দেবী পর্যন্ত আপনাকে না জানিয়ে গোপনে মেয়ের বাড়িতে পেল্লায় ভেট পাঠিয়েছেন, কাজটা কি তাঁর ঠিক হয়েছে বলুন! কে না জানে দাবার চালে একটু ভুল হওয়ায় আপনার বেয়াই রামশরণ সমাদ্দার আপনাকে অপমান করে গিয়েছিল এবং আপনাদের এখন মুখ দেখাদেখি নেই!”
“দ্যাখ হুলো, ওইসব বলে আমাকে ভেজাতে পারবি না। আজ কিন্তু আমি বজ্ৰাদপি কঠোর।”
“তা জানি কর্তামশাই। দুঃখ কী জানেন, বেড়ালের জন্য তো আর পেনাল কোড নেই। তাই হুলো হননের জন্য আপনার ফাঁসি হবে। কিন্তু হয়তো একদিন এই হুলোর জন্য আপনাকে হায় হায় করতে হবে। হয়তো হুলোকে আপনি ভুলে যেতে পারবেন না। চোর হোক, গুণ্ডা হোক, তবু হুলো যে আপনার কতবড় বন্ধু ছিল, তা একদিন আপনি বুঝবেন।”
“বিপাকে পড়লে অমন ভাল ভাল কথা সবাই বলে। কিন্তু আর সময় নেই রে হুলো। মনে মনে তৈরি হ, স্থির হয়ে দাঁড়া। এই দ্যাখ আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড, রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান…”।
“কিন্তু আপনিও মনে রাখবেন, যত বড় হও, তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও। আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়, এই কথা বলে যাব আমি চলে। গুডবাই কর্তামশাই।”
উদ্যত ঠ্যাঙার সামনে অসহায় হুলো। রাঘববাবুর চোখে জিঘাংসা, হুলোর মুখে আর্তি। ঠিক এই নাটকীয় মুহূর্তে হঠাৎ রাঘববাবুর বাঁ কানটা সুড়সুড় করে উঠল। তারপর ফিসফিস করতে লাগল। বিপদ! বিপদ! ফিসফিসের পর থিরথির। তারপর একেবারে থরথর করে কেঁপে উঠল রাঘববাবুর বাঁ কান। তিনি ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন। লক্ষণটা যে তাঁর খুবই চেনা। তাঁর শিথিল হাত থেকে ঠাস করে ঠ্যাঙাটা খসে পড়ল। তিনি ধীর পায়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।
হুলো দু’খানা মাছ মুখে নিয়ে এক লাফে বেরিয়ে এসে দোতলার বারান্দার রেলিং টপকে পাশের দেওয়ালের ওপর গিয়ে উঠে পড়ল এবং সেখান থেকে রাঘববাবুর উদ্দেশে নানারকম ব্যঙ্গবিদ্রূপ বর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু আজ আর সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করলেন না রাঘববাবু। সোজা বৈঠকখানায় এসে ধপ করে নিজের গদি-আঁটা চেয়ারখানায় বসে খুব গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।
ভাবনারই কথা কিনা। দুনিয়ায় অনেক ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। যেমন, হয়তো রাত্রে রোদ উঠল, আর দিনে জ্যোৎস্না। জলের মাছ আকাশে উড়তে লাগল, চড়াইপাখি গিয়ে বাসা বাঁধল পুকুরের জলে। এমনও হয়তো দেখা যাবে যে, গ্রীষ্মকালে দুর্গাপুজো, মাঘ মাসে রথ আর ফায়ূনে অম্বুবাচী হচ্ছে। কে জানে হয়তো জষ্টিমাসে লোকে লেপ গায়ে দেবে, পৌষমাসে হাতপাখা নেড়ে খাবে বরফজল। ডাঙায় এরোপ্লেন ঘুরে বেড়ালে, আর আকাশে গোরুর গাড়ি উড়লেও অবিশ্বাসের কিছু নেই। কিন্তু তা। বলে রাঘববাবুর বাঁ কানের কথা কিন্তু মিথ্যে হওয়ার নয়। বিপদ আসছে। তবে সেটা কোথা দিয়ে কী রূপ ধরে আসে, সেটাই চিন্তার কথা।
আনমনে হাত বাড়াতেই তামাকের নলটা তাঁর হাতে চলে এল।
কিছুক্ষণ খুব নিবিড়ভাবে তামাক খেলেন রাঘববাবু। তারপর আপনমনে বলে উঠলেন, “খুবই চিন্তার কথা!”
সঙ্গে-সঙ্গে একটা প্রতিধ্বনি হল, “খুবই চিন্তার কথা।”
প্রতিধ্বনি শুনে একটু অবাক হলেন রাঘববাবু। কোথাও কোথাও প্রতিধ্বনি হয়, একথা তিনি জানেন। তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু তাঁর যতদূর মনে পড়ছে এই বৈঠকখানায় তিনি কখনও প্রতিধ্বনি শোনেননি। তবে কি এতকাল ব্যাপারটা খেয়াল করেননি তিনি! একটু অবাক হয়ে নিজের হাতের তামাকের নলটিও দেখলেন রাঘববাবু। যতদূর জানেন, নবকৃষ্ণ বাড়ির লেপলোশক রোদে দিতে ছাদে বহাল আছে। সুতরাং নবকৃষ্ণর পক্ষে তামাক সেজে দেওয়া সম্ভব নয়। আর নবকৃষ্ণ ছাড়া তাঁর তামাক সাজার হুকুম আর কারও ওপর নেই। অথচ তিনি দিব্যি তামাক খাচ্ছেন! আরও একটু অবাক হয়ে তিনি হাতের নলটার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, “আমি তামাক খাচ্ছি!”
“আজ্ঞে, তামাক বলেই তো মনে হচ্ছে। অম্বুরি তামাকের গন্ধটাও ছেড়েছে ভাল।”
এবার সচকিত হয়ে পিছনে তাকিয়ে তিনি লোকটাকে দেখতে পেলেন। হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, “তুমি কে বলল তো!”
“আজ্ঞে, অধমের নাম গোলাপ রায়। আপনারই চরণাশ্রিত। কর্তা কি চিনতে পারছেন না আমাকে?”
রাঘববাবু মাথাটাথা চুলকে বললেন, “কী জানো, এত লোক আমার চরণাশ্রিত যে, তাদের সবাইকে মনে রাখা মুশকিল।”
“তা তো হতেই পারে। আমি হলুম গে মকরধ্বজের গোলাপ রায়। বেশি নয়, মাত্র আড়াই লক্ষ লাইট ইয়ার দূরের লোক।”
“ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তা বাপু, এখানে তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো! সব ঠিক আছে তো!”
“যে আজ্ঞে, অসুবিধে যা আছে তা গায়ে না মাখলেই হল। ধরুন, মকরধ্বজে আমরা সকালে জিলিপি আর লুচির জলখাবার খেতুম, এখানে রুটি আর কুমড়োর ঘ্যাঁট। মকরধ্বজে দুপুরে পোলাও মাংস আর পায়েস বাঁধা ছিল, এখানে ডাল ভাত ঘ্যাঁট আর মাছের ঝোল। আরও শুনবেন কি কর্তামশাই?”
“তা শুনতে তো মন্দ লাগবে না, বলে ফেলো।”
“রাতের খাবারটা মকরধ্বজে একটু ভারী রকমেরই হয়। একেবারে মোগলাই। বিরিয়ানির সঙ্গে তন্দুরি মুর্গি, পাকা মাছের কালিয়া, রোগন জুস, রেজালা, আলুবখরার চাটনি আর ক্ষীর। ফাঁকে ফাঁকে ছোটখাটো পদও থাকে। তা সেগুলোর কথা বলে আর ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করব না। সে তুলনায় এখানে রাতের খাবারটা বেশ হালকা, পেঁপের ঝোল আর ভাত।”
“তা হলে তো তোমার এখানে বেশ অসুবিধেই হচ্ছে হে!”
“না, কর্তামশাই, অসুবিধে কীসের? কথায় আছে পড়েছ মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। যখন যেমন, তখন তেমন। গুরুভোজন বাদ যাওয়ায় পেটের বিশ্রামও তো হচ্ছে।”
“তা বটে। তবে বাপু, তোমার তামাক সাজার হাতটা বেশ ভাল, বলতে কী আমাদের নবকৃষ্ণও এত ভাল সাজতে পারে না।”
“ওকথা বলে আর লজ্জা দেবেন না। দুটো কাজের কথা কইতে এসে দেখি আপনি খুব ভাবনায় পড়েছেন। তাই ভাবলুম ভাবনাচিন্তা করার সময় তামাক খুব কাজ দেয়।”
“বাঃ বাঃ, তোমার মাথায় তো বেশ ভাল ভাল ভাবনা আসে!”
মুখোনা করুণ করে গোলাপ রায় বলল, “আজ্ঞে, ওইটেই হয়েছে মুশকিল, মাথাই যে আমার শত্তুর। ভাল ভাল ভাবনাচিন্তা, মাপজোক আসে বলে এ মাথার জন্য লোকে লাখো লাখো টাকা দাম দিতে চায় বটে, কিন্তু তাতে শত্রুপক্ষের তো খুশি হওয়ার কথা নয়।
তাই তারা চায় আমাকে নিকেশ করতে। কর্তামশাই, ভাল মাথার যেমন দাম আছে, তেমনি আবার গুনোগারও আছে।”
রাঘব অবাক হয়ে বললেন, “কেন হে, তোমাকে নিকেশ করতে চায় কেন?”
“তাদের দোষ নেই কর্তামশাই, কারও বাড়া ভাতে ছাই দিলে বা মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে নিকেশ তো করতে চাইবেই। গোলাপ রায়
যে তাদের পথের কাঁটা!”
“কেন হে, তুমি করেছটা কী?”
“সেটা আর ভেঙে বলতে বলবেন না কর্তামশাই। আমার বড় বিপদ। দু-চারদিনের মধ্যেই একটা এসপার-ওসপার হয়ে যাবে।
আর সেইজন্যই আপনার কাছে আসা।”
“তা বাপু, বিপদ বুঝলে পুলিশের কাছে যাচ্ছ না কেন? আমাদের গিরিধারী দারোগা তো দাপটের লোক।”
একটু বিজ্ঞের হাসি হেসে গোলাপ বলল, “দারোগা পুলিশের কর্ম নয় কর্তামশাই। সাধারণ চোর-ডাকাত-খুনি হলে কি আর ভাবনা ছিল! আপনার আশীর্বাদে ওসব ছোটখাটো অপরাধী গোলাপ রায়ের হাতের ময়লা। কিন্তু এরা অনেক উঁচু থাকের লোক। মকরধ্বজের উলটো গ্রহই হল চ্যবনপ্রাশ, সেখানে গিজগিজ করছে সব প্রতিভাবান শয়তান। তাদের সঙ্গে এঁটে ওঠা দায়! ফলে যে গন্ধমাদনটি এসেছে তাকে লক্ষ করেছেন তো? দেখবেন ডান কানটা বাঁ কানের চেয়ে ছোট। ওটাই হল চ্যবনপ্রাশের লোকদের লক্ষণ। কালও বুঝতে পারিনি বটে, কিন্তু আজ সকালের আলোয় ভাল করে লক্ষ করেই বুঝলাম, আমার শমন এসে গেছে।”
“কদম কোঙারের কথা বলছ নাকি হে? কিন্তু সে তো একজন সামান্য লেঠেল।”
“তাই বলেছে বুঝি? তা অমন কত কথাই বলবে। আসল কথা হল, লোকটা এসে গেছে। এখন হয় ও মরবে, না হয় আমি। আর সেইজন্য আপনার কাছে আসা।”
“তাই তো! তুমি তো বেশ চিন্তায় ফেলে দিলে হে!”
“নিজের প্রাণটা হাতে নিয়ে লোফালুফি করেই তো আমাকে বেঁচে থাকতে হয় কর্তামশাই! তাই বলছিলুম, গোলাপ রায় মরেছে শুনলেও দুঃখ করবেন না। এরকম কত প্রতিভাই তো অকালে নষ্ট হয়ে যায়। সব কুঁড়িতেই কি ফুল ফোটে, না কি সব বৌলেই আম হয়। আপনাদের কোন কবি যেন বলেছেন, যে-নদী মরুপথে হারাল ধারা? এ হল সেই বৃত্তান্ত।”
“তা বাপু, এর কি কোনও বিহিত নেই? আমরা পাঁচজন থাকতে তোমাকে তো বেঘোরে মরতে দেওয়া যায় না।”
সবেগে মাথা নেড়ে গোলাপ বলল, “না কর্তামশাই, আমার প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে আপনারা কেন বিপদ ডেকে আনবেন? ও কাজও করবেন না। ছাতা দিয়ে কি বজ্রাঘাত ঠেকানো যায় মশাই? শোলা দিয়ে তো আর লোহা কাটা যায় না! কখনও কি শুনেছেন ছুঁচ দিয়ে কেউ বাঘ মেরেছে?”
রাঘববাবু কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, “তা অবশ্য শুনিনি।”
“তবে! চ্যবনপ্রাশের নামই দেওয়া হয়েছে গুণ্ডা গ্রহ। সেখানে গণ্ডায় গণ্ডায় গুণ্ডা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানে চার কদম হাঁটতে না হাঁটতেই চারটে খুন, সাতটা রাহাজানি, বারোটা ছিনতাই দেখতে পাবেন। আর গুণ্ডাদের চেহারাই বা কী, মনে হবে সাতটা মহিষাসুরকে চটকে মেখে নিয়ে এক-একটা গুণ্ডা তৈরি করা হয়েছে। তাদের তুলনায় কদম কোঙার তো নস্যি। তাকে চ্যবনপ্রাশের কুলাঙ্গারই বলতে পারেন। তবু তারই এলেমটা দেখুন। কাল রাতে সে ওই অতবড় লাশ হাবু দাসকে নেংটি ইঁদুরের মতো তুলে আছাড় মেরেছে। গুণেন গায়েনকে পিঁপড়ের মতো টোকা
মেরে উড়িয়ে দিয়েছে।”
“বলো কী? কই কেউ তো আমাকে এসব জানায়নি!”
“আজ্ঞে, কার ঘাড়ে ক’টা মাথা? আপনারও জানার দরকার নেই। মনে করে নিন, কথাটা আমি বলিনি, আপনিও শোনেননি।”
“তাই তো হে! আমার বিপদে তো দেখছি ঘরে ঢোকার আগে পাপোশে পা মুছছে।”
“যে আজ্ঞে। কড়া নাড়া দিতে আর দেরি নেই। আর সেইজন্যই গা-ঢাকা দিয়ে আপনার কাছে আসা। হাট গোবিন্দপুর থেকে তল্পিতল্পা গোটানোর আগে আপনার কাছে একটা জিনিস গচ্ছিত রেখে যেতে চাই।”
“কী জিনিস বলো তো!”
“এই যে!” বলে ট্যাঁক থেকে একটা কাগজের মোড়ক বের করল গোলাপ রায়। সাবধানে পুরিয়াটা খুলে জিনিসটা এগিয়ে দিয়ে বলল, “বড্ড দামি জিনিস কর্তামশাই। এই ছোট্ট জিনিসটার জন্যই এতদূর থেকে ধাওয়া করে এসেছে কদম কোঙার।”
রাঘববাবু দেখলেন, মোড়কের মধ্যে একটা ছোট পাথর। মটরদানা সাইজ। রংটা লালচে।
“এটা কী পাথর হে? চুনি নাকি?”
হেঃ হেঃ করে হেসে উঠল গোলাপ। বলল, “চুনি! কী যে বলেন কর্তামশাই। আমাদের মকরধ্বজে যে মোরামের রাস্তাগুলো আছে। সেগুলো তো চুনির গুঁড়ো দিয়েই তৈরি হয়। যদি হিরের কথা বলেন তা হলে বলি, মকরধ্বজের পথেঘাটে মাটির ঢেলার মতো হিরে পড়ে থাকে, বাচ্চারা কুড়িয়ে নিয়ে ঢিল মেরে মেরে আম পাড়ে। আর পান্না! আমাদের চার-চারটে পাহাড় আছে আগাগোড়া পান্না দিয়ে তৈরি। না কর্তামশাই, না। এ চুনিটুনি নয়। সারা বিশ্বজগতে চার-পাঁচখানার বেশিই নেই। এ যার দখলে থাকবে, সে কুবেরকে চাকর রাখতে পারবে।”
“বটে!”
“একটু সাবধানে রাখতে হবে কর্তামশাই, কেউ টের না পায়।”
রাঘব দোনোমোনো করে বললেন, “এত দামি জিনিস বলছ। তা এটা রাখা কি ঠিক হবে?”
“কর্তামশাই, একথা ঠিক যে, রাহুর পিছু পিছু কেতুও ঘুরে বেড়ায়। কাজেই এ জিনিসের পিছু পিছু যে বিপদও ঘুরে বেড়াবে তাতে আর সন্দেহ কী? তবে আমার তো চালচুলো নেই, তার ওপর কবে যে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায় তার ঠিক কী? তখন যে এই কুবেরের ধন বেওয়ারিশ পড়ে থাকবে, নইলে শত্রুপক্ষের হস্তগত হবে। আমি বলি কী, আপনার কাছেই থাক। যদি আমি পটল তুলি তা হলে এটা আপনারই হয়ে গেল, তবু ভাবব একজন সজ্জনের ভোগে লেগেছে।”
লজ্জা পেয়ে রাঘববাবু বললেন, “না, না, সেটা ধর্মত, ন্যায্যত ঠিক হবে না। তোমার জন্য তো আমি তেমন কিছু করিনি যে, এত দামি জিনিসটা তুমি আমাকে এমনি দিয়ে ফেলবে!”
চোখ বড় বড় করে গোলাপ বলল, “করেননি মানে? হোক ঘ্যাঁট, হোক জলের মতো পাতলা ডাল, হোক পেঁপের ঝোল, তবু তা খেয়ে তো আমার প্রাণরক্ষা হয়েছে মশাই, প্রাণের চেয়ে দামি জিনিস আর কী আছে বলুন! তবে হ্যাঁ, বিবেক দংশন বলেও একটা ব্যাপার আছে। বিবেক হল কাঠপিঁপড়ের মতো। নচ্ছারটা জামাকাপড়ের মধ্যে কোথায় ঢুকে লুকিয়ে থাকে কে জানে! তারপর সময়মতো এমন কামড়ায় যে, কহতব্য নয়। আপনার হয়তো তখন মনে হবে, আহা, গোলাপ বেচারাকে শুধু পেঁপের ঝোল আর ঘ্যাঁট আর ডাল খাইয়েই বিদেয় করলুম, আর সে আমার কত বড় উপকারটা করে গেল।”
রাঘববাবু সোৎসাহে বলে উঠলেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ তো! কাঠপিঁপড়ের কামড় আমি খুব চিনি।”
“তাই বলছিলুম কামশাই, ও জিনিসের দাম তো আর আপনার কাছ থেকে আমি নিতে পারি না! টাকাপয়সায় ওর দামও হয় না। তবু ওই বিবেক হতচ্ছাড়ার হাত থেকে বাঁচতে হলে দশ বিশ হাজার যা পারেন দিলেই চলবে। দামটাম নয়, নিতান্তই বিবেকের মুখ আটকে রাখা আর কী। একরকম বন্ধক রাখা বলেই মনে করুন। আপনার কাছে আমার পাথর বন্ধক রইল, আর আমার কাছে আপনার বিবেক।”
রাঘববাবু করুণ মুখ করে বললেন, “সবই তো বুঝলুম বাপু। মনে হচ্ছে তুমি ন্যায্য কথাই বলছ। কিন্তু বিধু স্যাকরাকে একবার পাথরটা না দেখিয়ে তো টাকাটা ফেলতে পারি না। একবার একটা লোক যে পোখরাজ বলে কাঁচ গছিয়ে গিয়েছিল।”
হাঃ হাঃ করে হেসে গোলাপ বলল, “বিধু স্যাঁকরা? কর্তামশাই, আমার অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু অকৃতজ্ঞ নই। আপনি অন্নদাতা, আশ্রয়দাতা। ও জিনিসের কোনও দাম আমি আপনার কাছ থেকে নিতে পারব না। ও আপনি এমনিই রেখে দিন। শুধু দয়া করে বিধু স্যাকরাকে ডেকে পাঁচ কান করবেন না। একটু সাবধানে রাখবেন এই অনুরোধ।”
রাঘববাবু ফের একটু দোনোমোনো করে বললেন, “সাবধানে রাখতে বলছ! কোথায় রাখা যায় তাই ভাবছি।”
“কেন কর্তামশাই, গোপন কুঠুরি বা চোরা সিন্দুক নেই?” লজ্জা পেয়ে রাঘববাবু বললেন, “তা আছে বটে।”
“তবে চলুন, আমিই দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক কোথায় রাখলে জিনিসটা নিরাপদ থাকবে।”
“বলছ! তবে চলো।”
অন্দরমহলের দরদালান পেরিয়ে বাঁ দিকে মস্ত ঠাকুরঘর। সেই ঘরে ঠাকুরের সিংহাসনের আড়ালে একটা ছোট্ট চৌখুপির মতো গুপ্ত দরজা। সেটা চাবি দিয়ে খুলে ভিতরে ঢুকলেন রাঘববাবু। হাতে টর্চ, পিছনে গোলাপ রায়।
গুপ্ত কক্ষের ভিতরে অন্তত সাতখানা সিন্দুক। পুরু ইস্পাতের তৈরি, মজবুত জিনিস।
দেখেশুনে গোলাপ বলল, “না, ব্যবস্থা খুব একটা খারাপ নয়।”
“খারাপ নয় বলছ!”
“মোটামুটি ভালই। এবার একে একে সিন্দুকগুলো খুলে একটু টর্চটা ফোকাস করে ধরুন দেখি। কোথায় রাখলে সুবিধে হয় একটু পরীক্ষা করে দেখি।”
তা খুললেন রাঘববাবু। প্রত্যেক সিন্দুকেই বিস্তর ছোট বাক্স। তাতে সোনাদানা, টাকাপয়সা, হিরে-জহরত।
দেখেশুনে বাঁ ধারের মাঝখানের সিন্দুকটাই পছন্দ হল গোলাপের। বলল, “এটা মন্দ নয় মনে হচ্ছে। ইস্পাতটা পুরু আছে, তা ছাড়া তিনটে চাবিতে খোলে। না কর্তামশাই, এটাতেই রাখুন।”
রাঘববাবু পাথরটা সাবধানে একটা বাক্সে রেখে সিন্দুক বন্ধ করে বললেন, “বলি ওহে গোলাপ!”
“বলুন কর্তামশাই।”
“বলছিলাম কী, সত্যিই যদি তুমি মরেটরে যাও, তা হলে তো পাথরটা আমারই হবে, না কি?”
“যে আজ্ঞে। গোলাপ রায়ের কথার কোনও নড়চড় হয় না।”
“কিন্তু বাপু, তা হলে যে আমি তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকব। সেটা কি ভাল দেখাবে?”
“তা কেন কর্তামশাই, আপনার কাছেও তো আমার কিছু ঋণ আছে। ধরুন খাওয়া থাকা বাবদ হিসেব করলে দিনে যদি সাড়ে তেরো টাকাও ধরেন তা হলে গত তেতাল্লিশ দিনে দাঁড়াচ্ছে একুনে পাঁচশো আশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা। সেটা কি কম হল কর্তামশাই? তবে আপনার বিবেকের দায়িত্বটা আর আমার ওপর অর্শাচ্ছে না।”
একটু লাজুক মুখে রাঘব কয়েকখানা নোট নিয়ে বললেন, “নাও হে, একটা রাখো। দু’হাজার আছে।”
যেন ছ্যাঁকা খেয়ে হাতটা টেনে নিয়ে গোলাপ বলল, “করেন কী কর্তা! ও টাকা আপনি বরং কাঙাল ভিখিরিদের বিলিয়ে দেবেন। আমার অন্তিমকাল তো ধাঁ করে চলেই এল প্রায়। এখন আর টাকাপয়সা দিয়ে হবেই বা কী?”
“আহা, আচ্ছা না হয় পাঁচ হাজারই দিচ্ছি। নাও হে, এ দিয়ে ভাল মন্দ কিছু খেও।”
মাথা নেড়ে গোলাপ বলল, “আর লজ্জা দেবেন না কর্তা। তবে একটা কথা বলি।”
“কী বলবে হে?”
“গন্ধে গন্ধে কদম কোঙার ঠিক জায়গায় এসেছে বটে, কিন্তু এত জনের মধ্যে কোনটা আমি তা কিন্তু বুঝে উঠতে পারেনি। তবে বেশি দিন তো আর ছদ্মবেশ রাখা যাবে না। কিন্তু কতদিন আয়ু আছে তা
বুঝে খোরাকির টাকা নিই কী করে। ধরুন যদি আরও এক মাস বেঁচে থাকতে হয় তা হলে এ-বাজারে পাঁচ হাজারে কি ভালমন্দ খাওয়া চলবে?”
“আচ্ছা আচ্ছা, পুরো দশই দিচ্ছি। দয়া করে নাও ভাই।”
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোলাপ বলল, “আপনাকে দুঃখও দিতে পারি না কি না। দিচ্ছেন দিন। তবে যদি বেঁচে ফিরে আসি তা হলে এ-টাকার ডবল ফেরত দিয়ে পাথর নিয়ে যাব। ওটা এক মাসের সুদ বলে ধরবেন। দু’মাস হলে ত্রিশ হাজার, তিন মাস হলে চল্লিশ, এরকম রেটেই টাকা আপনার বাড়তে থাকবে।”
রাঘববাবু বিগলিত হয়ে বললেন, “বেশ তো! বেশ তো!”
“তা হলে আসি কর্তামশাই! আর যে ক’দিন এ বাড়িতে আছি মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যাব।”
গোলাপ রায় চলে যাওয়ার পর চোরকুঠুরি থেকে বেরিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন রাঘববাবু।
বৈঠকখানায় এসে নিজের চেয়ারে বসলেন। তারপর খুব ভাবতে লাগলেন।
৪. অস্বস্তিটা যে কোথায় হচ্ছে
অস্বস্তিটা যে কোথায় হচ্ছে তা বুঝতে পারছিলেন না নন্দলাল। তবে হচ্ছে। কখনও মনে হচ্ছে মাথায়, কখনও ভাবছেন বুকে, কখনও বা পেটে। অস্বস্তিটা যেন একটা ডেলা পাকিয়ে শরীরের এখানে ওখানে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুয়ে বসে কিছুতেই আরাম হচ্ছে না।
দুপুরে হরকালী কোবরেজের বাড়িতে হানা দিলেন।
হরকালী উঠোনে তাঁর ওষুধের বড়ি রোদে শুকোতে দিয়ে জলচৌকি পেতে বসে একটা লাঠি হাতে কাকপক্ষী তাড়াচ্ছেন। মাথায় ভাঁজ করা ভেজা গামছা।
“বলি, ওহে হরকালী!”
“নন্দলাল যে!”
“তোমার কোবরেজি বিদ্যের ওপর যদিও আমার আস্থা নেই, তবু নাড়িটা একটু দেখো তো! সকাল থেকে একটা অস্বস্তি হচ্ছে।”
“অস্বস্তি হচ্ছে! বলি ব্রাহ্মণভোজনের নেমন্তন্ন খেয়েছ নাকি কোথাও?”
“আরে না, আজকাল কি আর মানুষের দেবদ্বিজে সেরকম ভক্তি আছে?”
“বলি ফলারটলার সাঁটাওনি তো?”
“আরে না রে ভাই। সেসব নয়। সকালে মর্কটের মতো একটা লোকের মুখদর্শন করার পর থেকেই অস্বস্তিটা হচ্ছে বলে মনে হয়। তা তোমার আয়ুর্বেদে কী বলে হে? দর্শন শ্রবণ থেকেও কি মানুষের রোগভোগ হতে পারে?”
“তা হবে না কেন? খুব হয়। যত রোগের গোড়াই তো মন। বিকট গন্ধ শুকলে, ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখলে, বিদঘুঁটে শব্দ শুনলে নানারকম রোগভোগ হতে পারে। এসব হলে মন বিকল হয়ে যায় বলে শাস্ত্রে নানারকম প্রায়শ্চিত্তের বিধানও আছে। প্রায়শ্চিত্ত মানে পুনরায় চিত্তে গমন। তা মর্কটটা কে?”
“সেইটেই তো হয়েছে সমস্যা। মর্কটটাকে যে আমি কোথায় দেখেছি তা মনে করতে পারছি না। অথচ আমার স্মৃতিশক্তি তো দুর্বল নয়। আর সেইজন্যই সকাল থেকে অস্বস্তিটা হচ্ছে বলে মনে হয়।”
হরকালী খুব মন দিয়ে চোখ বুজে অনেকক্ষণ ধরে নন্দলালের নাড়ি দেখে বললেন, “এ তো উধ্ববায়ু বলে মনে হচ্ছে। বায়ু উধ্বগামী হলে অনেক সময়ে সাময়িক স্মৃতিভ্রংশের মতো হয়। গুরুতর কিছু নয়। তালুতে একটু মধ্যমনারায়ণ তেল ঠেসে পুকুরে ভাল করে ডুব দিয়ে স্নান করে ফেলো গে৷”
তাও করলেন নন্দলাল। কিন্তু তেমন স্বস্তি বোধ করলেন না। দুপুরে খেয়েদেয়ে উঠে নন্দলাল সবে একটু শুয়েছেন, অমনি নাতি এসে বায়না ধরল, “ও দাদু, আজ আমরা পুজো-পুজো খেলব যে, তোমার ভেঁড়া নামাবলীটা দাও।”
নন্দলাল বললেন, “পুজো-পুজো খেলবে বুঝি? তা বেশ তো! আজ কী পুজো হচ্ছে তোমাদের?”
“শ্মশানকালী।”
“ও বাবা! তা হলে তো গুরুতর ব্যাপার।”
নাতি গম্ভীর মুখে বলল, “বলিও হবে।”
“বলি! বাপ রে! তা কী বলি দেবে ভাই?”
“মানকচু। গোবিন্দ এই অ্যাত বড় দা এনেছে।”
মাথার ভিতর কী যেন একটা টিকটিক করছে নন্দলালের। অস্বস্তিটাও যেন দ্বিগুণ চৌগুণ হয়ে গেল। তাই তো! এরকম হচ্ছে কেন? নন্দলাল ফের বালিশে মাথা রাখতে গিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলেন।
মনে পড়ে গেছে! মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তিটাও উধাও হয়ে গেল।
বছরখানেক আগে এক সকালে একটা লোক এসে হাজির। ভারী বিনয়ী ভাব। রোগা চেহারা, মুখোনা সরু, চোখে ধূর্তামি। নাকের নীচে একফালি সূক্ষ্ম গোঁফ আছে, মাথায় লম্বা চুল।
“পেন্নাম হই ঠাকুরমশাই। আমার নাম সুধীর বিশ্বাস। বড্ড ঠেকায় পড়ে এসেছি। কাজটা একটু উদ্ধার না করে দিলেই নয়।”
লোকটাকে দেখে নন্দলালের বিশেষ পছন্দ হল না। তবু মোলায়েম গলাতেই বললেন, “কী ব্যাপার বাপু?”
“আজ রাতে আমাদের শ্মশানকালী পুজোটা করে দিতে হবে ঠাকুরমশাই।”
“কোথায় পুজো?”
“আগে বিদ্যেধরী পেরোলেই নবগ্রাম। তার কাছেই। আজ্ঞে, আমরাই এসে নিয়ে যাব। প্রণামী দক্ষিণা যা চাইবেন সব দেওয়া হবে।”
“ওরে বাপু, ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে বলে হুড়ো দিলেই তো হবে না। আমারও পাঁচটা কাজ আছে।”
“দোহাই ঠাকুরমশাই, আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। সব আয়োজন পণ্ড হবে। বড় আশা নিয়ে এসেছি। যাঁর পুজো করার কথা ছিল কাল থেকে তাঁর ভেদবমি হচ্ছে। শীতলবাবু তো খুবই ভেঙে পড়েছেন।”
“শীতলবাবুটি কে?”
“আজ্ঞে সবাই তাঁকে ল্যাংড়া শীতল বলেই জানে। গোটা পরগনা একডাকে চেনে।”
“কই বাপু, নামটা শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না!”
“আজ্ঞে, বিদ্যেধরীর ওপারেই তাঁর কাজকারবার। এপারে তাঁর নামটা বিশেষ ছড়ায়নি। ভারী দরাজ হাতের মানুষ।”
“তা আমি ছাড়া কি আর পুরুত নেই হে!”
“কী যে বলেন ঠাকুরমশাই! পুরুতের অভাব কী? তবে সবাই একবাক্যে বলল, ওহে বাপু, পুরুতের মতো পুরুত না হলে কালীপুজো করাই উচিত নয়। শ্মশানকালী কাঁচাখেকো দেবতা। মুরুব্বিরা একবাক্যে আপনার কথাই বলছে যে! শীতলবাবু এই আড়াইশোটি টাকা অগ্রিম পাঠিয়েছেন। বাকিটা পুজোর পর।”
গাঁ-গঞ্জের পক্ষে টাকাটা বেশ ভালই। একটু দোনোমোনো করে নন্দলাল রাজি হয়ে গেলেন।
লোকটা বলল, “বেলা তিনটে নাগাদ গোরুর গাড়ি চলে আসবে ঠাকুরমশাই। বিদ্যেধরীতে নৌকো তৈরি থাকবে। কোনও চিন্তা করবেন না। পুজো হয়ে গেলেই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব। শীতলবাবুর কথার নড়চড় হয় না।”
তা নড়চড় হল না ঠিকই, বেলা তিনটে তো ঠিক তিনটের সময়েই দিব্যি ঝকঝকে গোরুর গাড়ি এসে হাজির। নতুন ছই লাগানো। ভিতরে পুরু খড় বিছিয়ে তার ওপর তোশক পেতে এবং তারও ওপর ফরসা চাঁদর বিছিয়ে বেশ ভাল ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুধীর বিশ্বাস সারাক্ষণ নানারকম বিনয় বচন আওড়াতে লাগল।
বিদ্যেধরীতে বেশ বড় একখানা নৌকো বাঁধা ছিল। তাতেও আরামের ব্যবস্থা। নন্দলাল খুশিই হয়েছিলেন। আজকাল ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতের মান মর্যাদা ক’জনাই বা বোঝে?
নবগ্রামের ঘাটে নামার পর পালকির ব্যবস্থা। সেটাও কিন্তু অস্বাভাবিক লাগেনি নন্দলালের কাছে। কিন্তু পালকিতে যেতে যেতে ক্রমে বুঝতে পারছিলেন যে, পথ আর ফুরোচ্ছে না এবং তাঁকে বেশ গভীর জঙ্গলে নিয়ে আসা হয়েছে।
“ওহে সুধীর, এ যে জঙ্গল!”
“যে আজ্ঞে। এখানেই শীতলবাবুর আস্তানা কিনা।” নন্দলাল ভয়ে আর প্রশ্ন করতে সাহস পেলেন না। অজ্ঞাতকুলশীলের কথায় রাজি হওয়া যে ঠিক হয়নি তাও বুঝলেন। কিন্তু বসে বসে ইষ্টনাম জপ করা ছাড়া আর কীই বা করবেন?
লোকগুলো গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা চাতালের মতো জায়গায় তাঁকে নিয়ে এল। সেখানেই পুজোর আয়োজন হয়েছে। চারদিকে মশালের আলো। পালকি থামতেই বিশ-পঁচিশজন ষণ্ডামাকা লোক এসে ঘিরে ফেলল। নন্দলাল অভিজ্ঞ লোক। বুঝলেন এরা মানুষ সুবিধের নয়। তবে তারা নন্দলালকে খুবই খাতির করতে লাগল। ষণ্ডাদের মধ্যেও যার চেহারা আরও ভয়ঙ্কর সেই লোকটা যখন লেংচে লেংচে এসে তাঁকে প্রণাম করল, তখন নন্দলাল বুঝলেন, এই হল ল্যাংড়া শীতল।
শীতল গম্ভীর মানুষ। গলার স্বর বাজের মতো। বলল, “ঠাকুরমশাই, আজ পুজোটা প্রাণ দিয়ে করবেন। আমার একটা রিষ্টি আছে।”
নন্দলালের একটা গুণ হল, বিপদে পড়লে মাথাটা ঠাণ্ডা হয়। তিনি ঘাবড়ালেন না। কালীপুজো মেলাই করেছেন, কাজেই ও নিয়ে চিন্তা নেই। পুজোর আয়োজনে বসে গেলেন। কিন্তু একটা সন্দেহজনক ফিসফাস কানে আসছিল। প্রথমটায় ভাবলেন ভুল শুনেছেন। কিন্তু বারবার কথাটা কানে আসছিল বলে হঠাৎ সচকিত হলেন। আজ নরবলি হবে! আজ নরবলি হবে!’ শুনে তাঁর মেরুদণ্ড বেয়ে হিমশীতল স্রোত নেমে গেল। সর্বনাশ! এ কাদের পাল্লায় পড়লেন তিনি! তাঁর শরীরে কাঁপুনি উঠে যাচ্ছিল।”
সুধীর বিশ্বাস এক ফাঁকে এসে কানে কানে বলল, “ঠাকুরমশাই, আপনাকে আগে বলা হয়নি। বললে হয়তো আসতে সঙ্কোচ বোধ করতেন।”
“কী কথা বাপু?”
“এই আজ্ঞে, আমাদের শীতলবাবুর রিষ্টি আছে তো! খুব নাকি খারাপ ফাঁড়া। তাই এক জ্যোতিষী নিদান দিয়েছে, নরবলি দিলে রিষ্টি কেটে যাবে।”
নন্দলাল কাঁপতে কাঁপতে বললেন, “বাপু, সে আমার দ্বারা হওয়ার নয়।”
“না ঠাকুরমশাই, বলি তো আর আপনাকে দিতে হবে না। আপনি শুধু উচ্ছ্বগ্নটা করে দেবেন। আমাদের বলি দেওয়ার ভাল লোক আছে। ওই যে দেখুন না, শিমুল গাছের তলায় বসে আছে, ওর নাম হল নকুল সর্দার। খুব ডাকাবুকো লোক। শীতলবাবুর ডান হাত। মাথাটা একটু গরম, তা ছাড়া আর কোনও গণ্ডগোল নেই।”
নকুল সর্দারকে দেখে নন্দলালের মনে হয়েছিল, এরকম হৃদয়হীন লোক তিনি জীবনে দেখেননি। যেমন সাঙ্ঘাতিক ঠাণ্ডা চোখ, তেমনি দশাসই চেহারা। হাতে একখানা মস্ত খাঁড়া নিয়ে বসে আছে। স্থির, পাথরের মতো। নন্দলাল নকুলের দিকে একবারের বেশি দু’বার তাকাতে পারেননি।
পুজো সেদিন তাঁর মাথায় উঠেছিল। অং বং করে কী মন্ত্র পড়েছিলেন কে জানে। তারপর যখন বলি দেওয়ার জন্য হাত-পা বাঁধা একটা বছর পনেরো-ষোলো বয়সের ছেলেকে এনে ধড়াস করে হাড়িকাঠের সামনে ফেলা হল, তখন নন্দলাল যে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাননি সেটাই ভাগ্যের কথা।
কিন্তু নন্দলাল নিজেকে সামলে নিলেন। মনটাকে শক্ত করলেন, ভেবে দেখলেন, এই পরিস্থিতিতে বুদ্ধি ঠিক না থাকলে সর্বনাশ!
মনে মনে বুদ্ধি আঁটতে আঁটতে পুজোটা সেরে নিলেন কোনওক্রমে। তারপর বলি উৎসর্গ করার সময়ে বেশ শান্তভাবেই হাত-পা বাঁধা ছেলেটার কপালে সিঁদুর পরালেন। বললেন, “ওহে, নিখুঁত কিনা দেখে এনেছে তো! খুঁত থাকলে কিন্তু বলি হয় না।”
সুধীর বিশ্বাস তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, “আজ্ঞে ঠাকুরমশাই, দেখেশুনেই এনেছি। কোনও খুঁত নেই। হাত-পা সব ঠিকঠাক আছে।”
নন্দলাল গম্ভীর হয়ে বললেন, “তবু ভাল করে পরখ করে নেওয়া ভাল। খুঁত থাকলে বলির উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হবেই না, উলটে অভিশাপ লেগে যাবে। ওহে বাপু, কেউ একটা মশাল এনে তুলে ধরো দেখি!”
তাড়াতাড়ি চার-পাঁচটা মশাল এগিয়ে এল। উবু হয়ে বসে নন্দলাল ছেলেটার অসহায় মুখটা দেখতে দেখতে হঠাৎ দ্রুকুটি করে বলে উঠলেন, “কী সর্বনাশ! এর যে কষের একটা দাঁত নেই!”
কথাটা ডাহা বানানো। কষের দাঁত আছে কি নেই তা নন্দলাল দেখতেই পাননি। আন্দাজে একটা ঢিল ছুড়লেন মাত্র।
সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে একটা গর্জন উঠল, “অ্যাঁ! কী সর্বনাশ! দাঁত নেই?”
নন্দলাল দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বললেন, “না হে, এ বলি দিলে মহাপাতক হয়ে যাবে।”
চারদিকে একটা শোরগোল উঠল। কেউ আর ছেলেটার দাঁত পরীক্ষা করার ঝামেলায় গেল না। নকুল সর্দার একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠে এসে সুধীর বিশ্বাসের ঘাড়ে একটা বিশাল থাবা মেরে বলল, “আজ এই শয়তানটাকেও তা হলে বলি দেব।”
চারদিক থেকে সুধীর বিশ্বাসের ওপরেই আক্রোশটা এসে পড়ল। বেশ কয়েকটা চড়থাপ্পড় খেয়ে পিছু হটতে হল তাকে।
শীতল বলল, “তা হলে কী হবে ঠাকুরমশাই? পুজো কি পণ্ড হয়ে গেল?”
নন্দলাল মিষ্টি হেসে বললেন, “ওরে বাবা, পঞ্চাশ বছর ধরে পুজো করে আসছি, আমার পুজো কি পণ্ড হয়?”
“কিন্তু বলি হল না যে!”
“তারও ব্যবস্থা আছে। রোসো বাপু, পুঁথি খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি।”
এই বলে পুরোহিত সংহিতাখানা খুলে যে শ্লোকটা বেরোল সেটাই খানিকটা পড়ে বললেন, “বুঝলে তো! নরবলি স্থলে ছাগ ও মহিষ বলি স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। ফল একই হবে।”
“কিন্তু জ্যোতিষী যে বলল, নরবলি ছাড়া হবে না!”
“পূজা-পাঠ-হোম-যজ্ঞের জটিল পদ্ধতি ও নিয়ম তো জ্যোতিষীর জানার কথা নয় বাবা। জ্যোতিষশাস্ত্র পার হয়ে তবে তো সংহিতার রাজ্য। জ্যোতিষীরা নিদান দেয়, কিন্তু সেটা কার্যকর তো করে পুরোহিতরা। পুর বা জনগণের হিত বা মঙ্গল যারা করে তারাই তো পুরোহিত।”
“তা হলে দোষ হবে না বলছেন?”
“কিছু না, কিছু না। দোষ হলে আমি দায়ী থাকব। ও ছোঁড়াটাকে আটকে রেখে আর কর্মফল খারাপ কোরো না। ওকে বাড়ি পৌঁছে দাও, আর একটা পাঁঠা নিয়ে এসো।”
তাই হল। ছেলেটার বাঁধন খুলে দুটো ভীমাকৃতি লোক টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। নিখুঁত পাঁঠা জোগাড় করতে না পেরে কাছাকাছি বাথান থেকে একটা মোষ নিয়ে আসা হল। বলির সময় নন্দলাল চোখ বুজে রইলেন। মনে মনে ভাবলেন, এতবুমন্দের ভাল।
এক রাতে এক ঝলক দেখা, তাও অনেক লোকের মধ্যে; তবু নকুল সর্দারকে ভুলে যাননি নন্দলাল। এতদিন বাদে দেখে হঠাৎ চিনতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু এখন আর সন্দেহ নেই। রাঘববাবুর বাড়িতে কদম কোঙার নামে যাকে দেখেছেন, সে আসলে নকুল সর্দার।
৫. হলধরের উড়ুক্কু ঝাঁটা
হলধরের উড়ুক্কু ঝাঁটা যে একদিন সত্যিই উড়ে বেড়াবে তাতে রুইতন আর হরতনের কোনও সন্দেহ নেই। রোজই গিয়ে তারা কিছুক্ষণ হলধরের ঘরে বসে খুব মন দিয়ে ঝাঁটা তৈরির কাজ দেখে।
হলধর দুঃখ করে বলে, “আমাকে কেউ বিশ্বাস করে না, বুঝলে? সবাই ভাবে আমি একটা পাগল। কিন্তু যেদিন সত্যিই আমার ঝাঁটা উড়ে বেড়াবে সেদিন লোকে বুঝবে।”
রুইতন আর হরতনের হলধরকে অবিশ্বাস হয় না। তার কারণ, কিছুদিন আগে হলধর একটা ছোট্ট বিঘতখানেক লম্বা এরোপ্লেন তৈরি করেছিল। তাতে ছোট জেটও লাগিয়েছিল হলধর। সেটা উড়তে পারে বলে প্রথমটায় বিশ্বাস হয়নি তাদের। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যেদিন হলধর সেটা পরীক্ষা করার জন্য বাড়ির পিছনে
আগাছায় ঘেরা পতিত জমিতে নিয়ে গিয়ে চালু করল, সেদিন সেটা কিছুক্ষণ গোঁ গোঁ শব্দ করার পর হঠাৎ খানিকটা ছুটে গিয়ে সাঁ করে আকাশে উড়ে গেল। উড়ে গেল তো গেলই। কোথায়, কতদূর পর্যন্ত গিয়েছিল তা আর জানা যায়নি। এবোপ্লেনটা অনেক খুঁজেও আর পাওয়া গেল না। হলধর মাথা চাপড়ে দুঃখ করে বলেছিল, “ইস, বড় ভুল হয়ে গেছে। একটা লম্বা শক্ত সুতোয় বেঁধে ছাড়লে জিনিসটাকে উদ্ধার করা যেত।”
সেই থেকে হলধরের লুকনো প্রতিভার ওপর রুইতন আর হরতনের অগাধ বিশ্বাস। কাজেই দুই ভাই উড়ুক্কু ঝাঁটার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল। কাজও প্রায় শেষ। দু’-একদিনের মধ্যেই পরীক্ষা হওয়ার কথা। কিন্তু হঠাৎ আজ সকালেই শোনা গেল হলধরকে তার ঘরে পাওয়া যাচ্ছে না। ঝাঁটাগাছও নেই।
রুইতন বলল, “আমার মনে হয় এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে হলধরদা ঝাঁটায় চেপে কোথাও চলে গেছে। কিন্তু ফিরতে পারছে না। আমাদের চারদিকে খুঁজে দেখা উচিত।”
হরতন করুণ মুখে বলে, “ধর যদি আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় চলে গিয়ে থাকে?”
“না না, অতদূর যাবে না। হলধরা তো বলেছে, ওটা কম পাল্লার রকেট।”
সব শুনে ভূতনাথ মাথা নেড়ে চুপি চুপি বলল, “ওসব নয় গো খোকাবাবুরা, আসল বৃত্তান্ত শুনলে তোমাদের পিলে চমকে যাবে।”
“কী বৃত্তান্ত ভূতনাথদাদা?”
“ওই নরখাদকটা হলধরকে খেয়ে ফেলেছে। একেবারে চেটেপুটে।”
রুইতন অবাক হয়ে বলে, “কোন নরখাদক?”
হরতন একটু ছেলেমানুষ। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “রান্না করে খেয়েছে? না কাঁচা?”
ভূতনাথ একটু হেসে বলল, “ওরা কাঁচাই ভালবাসে। কর্তামশাই বড্ড ভালমানুষ কিনা, ভাল করে পরখ না করেই ঠাঁই দিয়ে ফেললেন। কাল হলধরকে খেয়েছে, আজ হয়তো হাবুকে খাবে। তারপর একে একে সবাইকে। আমার পালা কবে পড়ে কে জানে?”
রুইতন বলল, “যাঃ, কী যে বলো, ও তো লেঠেল। আমাদের লাঠি খেলা শেখাতে এসেছে।”
“লাঠি খেলা? দূর দূর? লাঠিখেলার ও জানেটা কী? লাঠিখেলা শিখতে চাও বুঝি? তা বেশ তো, আমিই তোমাদের শেখাবো খন!
রুইতন বলল, “তুমি লাঠি-খেলা জানো বুঝি?”
ভূতনাথ মাথা নেড়ে বলে, “তা জানি না বটে, তবে টক করে শিখে নেবোখন।”
“কার কাছে শিখবে?”
“সে আছে। অত গুহ্য কথা শুনে তোমাদের কাজ নেই। তবে কাউকে যদি না বলো তা হলে চুপি চুপি বলতে পারি।”
“বলো না ভূতনাথদা।”
গলা নামিয়ে ভূতনাথ বলল, “খুড়োমশাই যে মস্ত লেঠেল ছিলেন! খুড়োমশাই কে তা বুঝতে পারলে তো?”
“তোমার সেই পোষা ভূতটা বুঝি?”
“আহা, ওভাবে বলতে নেই। খুড়োমশাইয়ের অপমান হয়। আমার পোষা হতে যাবেন কেন? বরং আমিই ওঁর পুষ্যি।”
“তুমি যে বলো এ বাড়িতে অনেক ভূত! আমরা তো একটাও দেখাতে পাইনি!”
ভূতনাথ চোখ বড় বড় করে বলে, “বলো কী? এ বাড়িতে তো গিজগিজ করছে ভূত! পীতাম্বরমশাই, আন্নাকালী দেবী।”
রুইতন হেসে বলল, “ওসব তো নবুদার বানানো গল্প। আমরা
নবুদাকে জিজ্ঞেস করায় বলল, দূর দূর! ভূতনাথটা কর্তাবাবুর কাছে গুল মারছিল বলে ওকে ভড়কে দেওয়ার জন্য বলেছি।”
ভূতনাথ অবাক হয়ে বলল, “কিন্তু কর্তাবাবুও যে নবুদাদার কথায় সায় দিলেন!”
“নবুদার সব কথাতেই বাবা সায় দেয়। নবুদা হল বাবার মন্ত্রী।”
হরতন বলল, “মুখ্যমন্ত্রী, না রে দাদা?”
ভূতনাথ চিন্তিত হয়ে বলল “তা হলে তো মুশকিলেই পড়া গেল খোকাবাবুরা! ভূতের আশাতেই এতদূর আসা কিনা! কিন্তু এ বাড়িতে ভূত না থাকার তো কথা নয়! পুরনো বাড়ি, সাতপুরুষের বাস! আমার অঙ্কটা তো মিলছে না খোকাবাবুরা! ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হবে।”
সন্ধের পর দুই ভাই দোতলায় পড়ার ঘরে বসে লেখাপড়া করছিল। এমন সময় হঠাৎ হরতন চেঁচিয়ে উঠল, “জানালার বাইরে দিয়ে ওটা কী উড়ে গেল রে দাদা?”
রুইতন অবাক হয়ে বলল, “কী আবার উড়ে যাবে? প্যাঁচা বা বাদুড় হবে হয়তো।”
হরতন জানালার কাছে ছুটে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। তারপর উত্তেজিত হয়ে বলল, “দেখ দাদা দেখ, একটা লোক উড়ে বেড়াচ্ছে।”
“যাঃ,” বলে রুইতনও উঠে এল।
যা দেখল তা অবিশ্বাস্য। জ্যোৎস্না রাত্রিতে সত্যিই একটা বিরাট ফড়িঙের মতো জিনিস উড়ে বেড়াচ্ছে। তার পিঠে একটা মানুষ।
“এই দাদা, হলধরদা নয় তো?” বাগানে একটা চক্কর খেয়ে জিনিসটা সাঁ করে ফের জানালার কাছে চলে এল। ঘরের যেটুকু আলো বাইরে গিয়ে পড়েছে তাতে দেখা গেল, হলধরই বটে!হলধর একগাল হেসে তাদের দিকে চেয়ে হাত নেড়ে চেঁচাল, “মার দিয়া কেল্লা! মার দিয়া কেল্লা!”
“দেখলি দাদা!”
“সত্যিই তো!”
উড়ুক্কু ঝাঁটা ফের হুশ করে জানালার কাছে এসে ফের সাঁ করে বেরিয়ে গেল। হলধর শুধু চেঁচিয়ে বলল, “দারুণ মজা!”
দু’ভাই হাঁ করে দৃশ্যটা দেখছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল ঝাঁটাটা আর একপাক ঘুরে আসতে গিয়ে হঠাৎ ফুস শব্দ করে গোত্তা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল।
দুই ভাই দৌড়ে নেমে ছুটে পিছনের পোড় জমিটায় গিয়ে দেখল, হলধর বসে বসে বিকৃত মুখে উঃ-আঃ করতে করতে মাজায় হাত বোলাচ্ছে।
“তোমার খুব লেগেছে হলধরদাদা?”
“তা লাগবে না? বেশ ভালই লেগেছে। তবে জিনিসটা সাকসেসফুল হওয়াতে ব্যথা তেমন টের পাচ্ছি না। কিন্তু মুশকিল কী জানো, একবার উড়ে চললে ব্যাটা বশে থাকতে চায় না। বাগ মানানো খুব মুশকিল। সেইজন্য দু-চারটে যন্ত্রপাতি লাগানো দরকার। আর একটা অসুবিধে হল সরু লাঠির ওপর বসে থাকা কিন্তু বেশ কঠিন ব্যাপার। ভাবছি একটা সাইকেলের সিট বা ঘোড়ার জিন লাগিয়ে নেব।”
হরতন বলল, “তা হলে দুটো লাগিও। একটায় তুমি বসবে, আর একটায় আমি আর দাদা।”
“হ্যাঁ, হবে হবে, সব হবে। একবার আবিষ্কারটা যখন হয়ে গেছে তখন বাদবাকি ব্যবস্থা করা শক্ত নয়। এখন কাজ হল, ওই নরদানবের হাত থেকে জিনিসটাকে রক্ষা করা।”
হরতন বলে উঠল, “আচ্ছা হলধরদাদা, ভূতনাথদা যে বলছিল তোমাকে একটা নরখাদক খেয়ে ফেলেছে! তুমি ভূত হয়ে আসোনি তো!”
মুখটা ব্যথায় বিকৃত করে হলধর বলল, “না রে ভাই, এখনও ভূত হইনি, তবে হওয়া বিচিত্র নয়। নরদানবটা তো আমাকে নিকেশ করতেই এসেছে। সারাদিন বাঁশঝাড়ে লুকিয়ে ছিলুম। কী মশা রে ভাই সেখানে! পিঁপড়েও কামড়েছে অনেক। তবে কষ্ট সার্থক। চাট্টি মুড়িটুড়ি এনে দেবে খোকারা? বড্ড খিদে।”
দুই ভাই দৌড়ে গিয়ে মুড়ি নিয়ে এল। মুড়ি খেতে খেতে হলধর বলল, “আচ্ছা থোকারা, ঝাঁটায় চড়ে উড়ে বেড়ানোর সময় ছাদে একজন বিধবা থান পরা মেয়েছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। তার হাতে একটা খ্যাংরা ঝাঁটা। তিনি কে বলো তো! এই বাড়িতে বিধবা তো কেউ নেই!”
রুইতন মাথা নেড়ে বলল, “জানি না তো?”
“শুধু তাই নয়, আরও দেখলুম, পিছনের বারান্দায় একজন বুড়ো মানুষ খুব পায়চারি করছেন। হাতে মোটা লাঠি। তাঁর সাদা গোঁফ। ঠিক চিনতে পারলুম না। কে জানো?”
রুইতন বলল, “না তো!”
“তা হলে কি ভুল দেখলুম? তা তো হতে পারে না। আমার। চোখের দোষ নেই। আরও একটা কথা।”
“কী?”
“তোমাদের বাড়ির পিছনে ওই মস্ত আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে যে পুরনো দেউড়িটা রয়েছে, তার বন্ধ ফটকের বাইরে চারজন যামার্কা লোক দাঁড়িয়ে কী যেন গুজগুজ ফুসফুস করছিল। চোর ডাকাত হতে পারে। নবুদাদাকে একটু সাবধান করে দিও। আমি এখন আমার বাঁশঝাড়ে ফিরে যাচ্ছি।”
হরতন বলল, “কিন্তু বাঁশঝাড়ে তুমি শোবে কোথায়?”
“বাঁশপাতা পড়ে পড়ে সেখানে পুরু গদির মতো হয়ে আছে। শুয়ে ভারী আরাম।”
সন্ধের পর বাড়িটা একদম সুনসান হয়ে যায়। বাড়ির ঝি চাকররা বেশিরভাগই সন্ধের পর বাড়ি চলে গেছে। শুধু রান্নার ঠাকুর আর দু’জন জোগালি একতলার রান্নাঘরে কাজকর্ম করছে। গিন্নিমা শোয়ার ঘরে, কর্তামশাই বৈঠকখানায়, রুইতন আর হরতন পড়ার ঘরে। বিশাল দোতলাটা এ সময়ে হাঁ হাঁ করে।
ছাদে ওঠার সিঁড়ির নীচে ঘুপচি জায়গাটায় বসে নবকৃষ্ণ কর্তামশাইয়ের জন্য একমনে তামাক সাজছিল। টিকে ধরিয়ে ফুঁ দিয়ে সবে আগুনটাকে ধিইয়ে তুলেছে, ঠিক এমন সময় কে যেন বলল, “ওটা কিন্তু তোর খুব খারাপ ওভ্যেস।”
নবকৃষ্ণ যখন যে কাজ করে তাতেই অখণ্ড মনোযোগ, তাই আনমনে বলল, “কোন ওভ্যেসটা?”
“ওই যে ফুঁ দিয়ে কলকে ধরাস! ফুঁ দিলে যে জিনিসটা এঁটো হয় সে খেয়াল আছে? কবে যে তোদের আক্কেল হবে কে জানে! বাছাকে আমার এঁটোকাঁটা খাওয়াচ্ছিস, তাতে কি তোর ভাল হবে?”
নবকৃষ্ণ কলকেটা প্রায় ধরিয়ে ফেলেছে। অন্যমনস্ক না হয়ে বলল, “ওসব ছোটখাটো দোষ ধরবেন না। আগুনে দোষ নেই। অগ্নিশুদ্ধ হলে সব শুদ্ধ।”
“বলি কথা তো মেলাই শিখেছিস দেখছি। এত শাস্ত্রজ্ঞান কবে থেকে হল?”
কলকেটা ধরিয়ে ফেলে এবার নবকৃষ্ণ মুখ তুলে চেয়ে দেখল, ছাদের সিঁড়িতে এক বিধবা ঠাকরুন দাঁড়িয়ে। পরনে থান, মাথায় কদমছাঁট চুল, চোখ দুখানায় খুব তেজ। তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে বলল, “পেন্নাম হই মা ঠাকরুন, তা কোথা থেকে আসা হচ্ছে?”
“কোথা থেকে আবার আসব রে মুখপোড়া? আমার কি কোথাও যাওয়ার জো আছে? মায়ার বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি, আজও উদ্ধার পেলুম না।”
নবকৃষ্ণ গদগদ হয়ে বলল, “যা বলেছেন মা ঠাকরোন। মায়া হল কাঁঠালের আঠা, সহজে ছাড়তে চায় না। বড় চটচটে জিনিস। তা মা ঠাকরোন, কর্তাবাবুকে খবর দেব, না গিন্নিমাকে? আপনি কোন তরফের লোক তা তো ঠিক জানা নেই কিনা।”
“কেন রে হাঁদারাম, জানা নেই কেন? পাঁচ কুড়ি বছর ধরে ঘাঁটি গেড়ে বসে নিত্যি তোদের অনাছিষ্টি দেখছি, আমি কি উটকো লোক রে অলপ্পেয়ে? শুদ্ধাচার লোপাট হয়েছে, গোবর গঙ্গাজলের তো বালাই-ই নেই, তুলসীমঞ্চে কেউ একবার সাঁঝের পিদিমটা অবধি জ্বালে না। যত দেখছি তত গায়ে জ্বালা হচ্ছে। এর চেয়ে বরং ট্যাঁশদের খাতায় গিয়ে নাম লেখা, বালাই চুকে যাবে।”
লজ্জা পেয়ে মাথা চুলকে নবকৃষ্ণ বলে, “সেসব ছিল বটে সব ঠাকরোন, তবে কে করে বলুন! দোষঘাট নেবেন না, আপনি তো এসেই গেছেন, এখন থেকে সব আগের মতোই হবে’খন। তা রাত্তিরে কী খাবেন বলুন দেখি! দুধ আছে, মর্তমান কলা আছে, খান্দেসরি চিনি আছে, চারটি সাগুটা ভিজিয়ে রাখব কি?”
ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মহিলা বললেন, “আর খাওয়া! সে তো কতকাল আগেই ঘুচে গেছে। আর খেলেও কি তোদের মতো অনাচারী ম্লেচ্ছদের হাতে খাব নাকি রে নচ্ছার? হেগোবাসী ছাড়ার বালাই অবধি ঘুচিয়ে দিয়ে বসে আছিস। নরকে যাবি যে!”
নবকৃষ্ণ ভারী কাঁচুমাচু হয়ে বলে, “সে তো বটেই মা ঠাকরোন। পাপের বোঝা নিত্যি ভারী হচ্ছে।”
মহিলা একটু নরম গলায় বললেন, “তা হ্যাঁ রে, আমাকে কি সত্যিই চিনতে পারলি না?”
মাথা চুলকে নবকৃষ্ণ লাজুক মুখে বলল, “চেনা চেনা ঠেকছে মা ঠাকরোন, তবে বুড়ো হচ্ছি তো, স্মৃতিভ্রংশ মতো হয়।”
“তবে যে ভূতনাথের কাছে আমার নামে গল্প ফাঁদলি! খুব যে বললি, আন্নাকালী দেবী এ বাড়ির আনাচেকানাচে ঘোরে।”
একগাল হেসে নবকৃষ্ণ বলে, “সে আর কবেন না মা ঠাকরোন, ভূতনাথটা বড্ড মিথ্যেবাদী। ভূতের গপ্পো ফেঁদে বসেছিল কর্তাবাবুর কাছে। উনি তো আবার ভালমানুষ লোক, যে বলে বিশ্বাস করে ফেলেন। তাই ভূতনাথকে ভড়কে দেওয়ার জন্য বানিয়ে ছানিয়ে বলেছিলাম আর কী। পীতাম্বরমশাই, হরুখুড়ো, পঞ্চা বিশ্বাস, আন্নাকালী দেব্যা…”
মহিলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “বানিয়ে বলেছিলি বটে, কিন্তু মিথ্যে বলিসনি রে।”
“তা মা ঠাকরোন, আপনি এসব জানলেন কী করে? ভুতোটা বলেছে বুঝি?”
“না, ভূতনাথ বলবে কেন? আমি তো সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কানেই শুনেছি।”
ভারী অবাক হয়ে নবকৃষ্ণ বলল, “কিন্তু মা ঠাকরোন, সেখানে যে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না!”
“কে বলল ছিল না? না থাকলে শুনলুম কী করে রে হতভাগা? এখনও কি তোকে বলে দিতে হবে যে, আমিই আন্নাকালী দেব্যা?”
“অ্যাঁ।”
“হাঁ করে রইলি যে বড়! বলি আকাশ থেকে পড়লি নাকি?” নবকৃষ্ণের হাত থেকে কলকে পড়ে গেল। সে মেঝেয় পড়ে চোখ উলটে গোঁ গোঁ করতে লাগল।
আন্নাকালী ভারী বিরক্ত হয়ে বললেন, “আ গেল যা! এ যে দাঁতকপাটি লেগে ভিরমি খেল। একটা কাজের কথা বলতে এলাম, দিল সব ভণ্ডুল করে। এখন যে কী করি!”
পিছনের ফটকে ডাকাত পড়ার খবরটা দিতে এসে রুইতন আর হরতনই নবকৃষ্ণকে ওই অবস্থায় দেখতে পেল।
কাছে গিয়ে হরতন নবকৃষ্ণের অবস্থা দেখে বলল, “দাদা, নবুদা শুয়ে শুয়ে গান গাইছে কেন রে?”
“ধ্যাৎ, নবুদা কখনও গানটান গায় না।”
“তা হলে কি নাক ডাকছে?” রুইতন একটু বড়। তার বুদ্ধি বিবেচনা হয়েছে। সে দেখেটেখে বলল, “না, নবুদা বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে। বাবাকে খবর দিতে হবে।”
খবর পেয়ে রাঘববাবু এলেন, অন্য লোকজনও এসে গেল। চোখে মুখে জল ছিটোবার পর নবকৃষ্ণ চোখ মেলেই ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে বলল, “আমি দেশে যাব কর্তাবাবু, আমাকে ছুটি দিন।”
“কেন রে, কী হল হঠাৎ?”
এ ভূতের বাড়িতে আর থাকব না। রাঘববাবু অবাক হয়ে বললেন, “ভূতের বাড়ি! বলিস কী? এ বাড়িতে এক জন্ম কাটিয়ে দিলি, কখনও ভূতটুত দেখেছিস?”
“কিন্তু আজ যে স্বয়ং আন্নাকালী দেব্যা দেখা দিয়েছেন।”
“দূর বোকা! কী দেখতে কী দেখেছিস!”
উঠে বসে মাথা নেড়ে নবকৃষ্ণ বলল, “শুধু দেখা নয় কর্তাবাবু অনেকক্ষণ কথাবার্তাও হয়েছে। ভুল দেখা টেখা নয়।”
রাঘববাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, “তাই তো রে! তা আন্নাপিসি চায় কী? গয়ায় পিণ্ডি দিতে হবে নাকি?”
জড়ো-হওয়া লোকজনের ভিতর থেকে পরিপাটি ধুতি আর পাঞ্জাবি পরা সরুমতো একটা লোক এগিয়ে এল। লোকটার সবই সরু। শরীর সরু, মুখ সরু, নাক সরু, গোঁফ সরু এবং এমনকী চোখের ধূর্ত চাউনিটা অবধি সরু।
জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে লোকটা বিনয়ী গলায় বলল, “পেন্নাম হই কর্তামশাই। আপনার তো বেশ ঝাট যাচ্ছে দেখছি।”
রাঘব একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, “তা যাচ্ছে বটে! তা তুমি কে?”
“অধমের নাম সুধীর বিশ্বাস। ধামের কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। যখন যেখানে তখন সেখানে। পেটের ধান্ধায় ভেসে ভেসে বেড়াই আর কী!”
“অ। তা কী চাও বাপু?”
“আজ্ঞে একটা কথা বলতে আসা। ফাঁক বুঝে বলব বলেই এসেছিলাম। তা এসে দেখি কী একটা হাঙ্গামা হচ্ছে। তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। জুত মতো বলার জন্য আরও একটু দাঁড়িয়ে থাকলে বোধ হয় ভালই হত। কিন্তু ঝোঁপ বুঝে কোপ মারার মতো বরাত আর ক’জনের হয় বলুন! হাতে আর তেমন সময়ও নেই কি না।”
“তা তো ঠিকই হে। তা কথাটা কী নিয়ে বলো তো?”
লোকটা চারদিকে চেয়ে যেন একটু অবাক হয়েই বলল, “কর্তামশাই, খোকা দুটিকে দেখছি না তো!”
“খোকা! কোন খোকা হে?”
“আপনার খোকা দুটির কথাই বলছি। রুইতন আর হরতন। আহা, বড় ভাল দুটি ছেলে হয়েছে আপনার। যেন দেবশিশু। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।”
“তারা এখন পড়ার ঘরে।”
“ভাল, ভাল। লেখাপড়া শিখে মানুষ হওয়া খুব ভাল। পেটে বিদ্যে, ঘটে বুদ্ধি না থাকলে এই আমাদের মতো অকাজ-কুকাজ করে বেড়াতে হবে। সব ভাল যার শেষ ভাল। যা দিনকাল পড়েছে, খোকা দুটিকে একটু সামলে রাখবেন।”
“সে তো বুঝলাম, কিন্তু তোমার আসল কথাটা কী?”
ভারী অপরাধী মুখ করে মাথা নুইয়ে, হাত কচলে সুধীর বিশ্বাস বলল, “আছে, সেটা পাঁচজনের সামনে বলার মতো নয়। একটু গুহ্য কথা। যদি একটু ফাঁকে আসেন তা হলে সাহস করে বলে ফেলি।”
“অ, তা এসো, ফাঁকেই এসো।”
বৈঠকখানায় ঢুকে চারদিকে চেয়ে সুধীর বিশ্বাস বলল, “বাঃ, বেশ বৈঠকখানাটি আপনার। এসব ঘরে বাস করলে মনটাও উঁচু থাকে। মেজাজও ভাল হয়।”
“সে তো বুঝলুম, কিন্তু কথাটা কী?”
“এই যে বলি। কোন মুখে বলব সেইটেই ভাবছি। বড় কথা ছোট মুখে কেমন মানাবে, সেটাও চিন্তার বিষয়।”
“অত সঙ্কোচ কীসের হে? বলে ফেললেই ল্যাটা চুকে যায়।”
ঘাড়টাড় চুলকে, লজ্জার হাসি হেসে, হাত-টাত কচলে সুধীর বিশ্বাস বলল, “কর্তামশাই, লাখপাঁচেক টাকা হবে?”
রাঘব হাঁ হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থেকে বললেন, “কী বললে হে? ঠিক শুনেছি তো!”
সুধীর বিশ্বাস মাথা নিচু করে বলল, “আজ্ঞে, একবার বলতেই মাথা কাটা গেছে। দু’বার পেরে উঠব না। ভারী লজ্জা করবে না আমার। তবে বলি, ঠিকই শুনেছেন।”
“পাঁচ লাখ টাকা! তার মানে কী?”
সুধীর বিশ্বাস ভারী সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, “আজ্ঞে পাঁচ লাখ টাকার মানে পাঁচ লাখ টাকা বলেই তো মনে হচ্ছে। না হয় ডিকশনারিটা একটু দেখে নিন।”
“বলি পাঁচ লাখ টাকা আছে কিনা জেনে তোমার কাজ কী?”
সুধীর বিশ্বাস লজ্জার হাসি হেসে বলল, “আজ্ঞে, আমার আর কাজ কী? পাঁচ লাখ টাকা কেন, আমি পঞ্চাশ টাকারই হিসেব গোলমাল করে ফেলি। আর পাঁচ লাখ পেলেই বা রাখব কোথায়? চালচুলো নেই, চোরে ডাকাতে কেড়ে নেবে।”
“তা হলে পাঁচ লাখ টাকার কথা উঠছে কেন?” হাতজোড় করে সুধীর বিশ্বাস বলে, “সে আমার জন্য নয় কর্তামশাই।”
“তা হলে?”
“শ্রদ্ধাস্পদ ল্যাংড়া শীতলের জন্য। তিনি বলে পাঠিয়েছেন, গরিব দুঃখীদের তো আপনি কতই বিলিয়ে দেন। তাঁকেও না হয় দিলেন। দান-ধ্যান না করলেও চলবে। দীর্ঘমেয়াদী হাওলাত হিসেবে দিলেও ক্ষতি নেই। ধরুন বছর পঞ্চাশেক পর থেকে তিনি দু’-পাঁচ টাকা করে শোধ দিতে শুরু করবেন।”
“বলি তুমি পাগলটাগলনও তো!না কি ইয়ার্কি মারতে এসেছ?” জিভ কেটে, নিজের দু’খানা কান স্পর্শ করে সুধীর বিশ্বাস বলল, “আজ্ঞে, ইয়ার্কি মারব কী কর্তামশাই, আপনার সঙ্গে কথা কইতে যে আমার হাঁটুতে হাঁটুতে কত্তাল বাজছে! মান্যিগন্যি লোকেদের সঙ্গে কথা বলার কোন যোগ্যতাটা আছে আমার?”
“এই ল্যাংড়া শীতলটা কে?”
“আজ্ঞে, শ্রদ্ধেয় শীতলদাদাও একজন মান্যগণ্য লোক। তবে তাঁর এখন খারাপ সময় যাচ্ছে। একটা কঠিন ফাঁড়া আছে সামনে। তাই বড় নেতিয়ে পড়েছেন। ব্যবসাবাণিজ্য লাটে উঠেছে।”
“পাঁচ লাখ টাকা চেয়ে পাঠায়, তার বেজায় বুকের পাটা দেখছি!”
“যে আজ্ঞে যথার্থই বলেছেন। আমাদের শীতলদাদা অবস্থার বিপাকে পড়লেও ওই একটা জিনিস এখনও আছে। তা হল বুকের পাটা।”
“এখন এসো গিয়ে। আমার অনেক কাজ আছে।”
“যে আজ্ঞে। তা হলে শীতলদাদাকে গিয়ে কী বলব?”
“বোলো, টাকা অত শস্তা নয়।”
“আজ্ঞে, তাই বলব। তা হলে আমি আসি গিয়ে।”
“এসো।”
“তা কামশাই, যাওয়ার আগে আপনার খোকা দুটিকে একবারটি একটু আদর-টাদর করে যেতে পারি কি?”
“না হে, তারা লেখাপড়া করছে।”
ঠিক এই সময়ে পাঁচু ধেয়ে এসে বলল, “কর্তাবাবু, ছেলে দুটোকে যে গুণ্ডারা তুলে নিয়ে গেল!”
রাঘব সটান হয়ে বললেন, “অ্যাঁ!”
“হ্যাঁ কর্তাবাবু! পিছনের মাঠে তুবড়ি ফুটছে দেখে দুই ভাই নীচে নেমে দেখতে গিয়েছিল। রতন নিজের চোখে দেখেছে, তিন-চারটে মুশকো জোয়ান রুইতন আর হরতনকে ধরে কাঁধে ফেলে হাওয়া হয়ে গেছে।”
“সর্বনাশ! শিগগির লেঠেলদের খবর পাঠা। কোথায় নিয়ে গেল দেখ, কী সব্বোনেশে কাণ্ড!”
সুধীর বিশ্বাস যাই-যাই করেও যায়নি। ভারী জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ানো, তার দিকে চোখ পড়তেই রাঘব হুঙ্কার ছাড়লেন, “এ কি তোমার কাজ?”
মাথা নেড়ে সুধীর বিশ্বাস বলল, “আজ্ঞে না। কাজ সব ভাগ করা আছে কিনা।”
“তার মানে?”
“যার যে কাজ। আমার কাজ ছিল আপনার কাছে কয়েকটা কথা নিবেদন করার। তার বেশি নয়।”
“ওরা কারা?”
“আজ্ঞে, শিবেন, কাদু আর তাঁপা। ওগুলো ওদের আসল নাম নয় অবশ্য। তবে ওই নামেই ডাকে।”
রাঘববাবু হুঙ্কার ছাড়লেন, “ওরে কে আছিস, শিগগির আয়। এটাকে ধরে চোর কুঠুরিতে নিয়ে বেঁধে রাখ।”
সুধীর বিশ্বাস অতিশয় দুঃখের সঙ্গে বলল, “বিপদে পড়লে লোকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না কর্তামশাই। সেটা দোষেরও নয়। তবে কিনা থাকলে ভাল হত।”
“তার মানে?”
“ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভাবুন কর্তামশাই। শীতলদাদা তো ধার হিসেবেই চাইছেন। শোধ দিতে একটু দেরি হবে এই যা।”
৬. রোদটা একটু পড়তেই
রোদটা একটু পড়তেই নন্দলাল বেরিয়ে পড়লেন। কর্তাবাবুকে খবরটা একটু দেওয়া দরকার। নকুল সর্দারের মতো লোক তো বিনা কারণে রাঘব চৌধুরীর বাড়িতে ঢোকেনি। পিছনে ল্যাংড়া শীতলের মতো সাঙ্ঘাতিক লোকও আছে।
বাড়ির পুবধারে বাবলা গাছের জড়ামড়ির ভিতর দিয়ে নির্জন সরু রাস্তা। এ-রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই হয়। আরও খানিকটা গেলে বাঁশবন, তারপর খানিক পতিত জমি পার হলে রাঘববাবুর বাড়ির চৌহদ্দি শুরু হয়েছে।
সরু রাস্তায় পা দিতেই সামনে একটা লোক যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হল। রোগা চেহারা, সরু গোঁফ, তেলচুকচুকে চুলে নিখুঁত টেরি। মুখে সেইরকমই বশংবদ হাসি আর বিনয়।
“পেন্নাম হই ঠাকুরমশাই! চিনতে পারছেন?”
খুব চিনতে পেরেছেন নন্দলাল। চিনতে পেরে হাত পা-ঠাণ্ডা মেরে আসছিল তাঁর।
“কী চাও বাপু?”
“আজ্ঞে, আমি সুধীর বিশ্বাস। চিনতে পারলেন না? তেরো মাস আগে একবার এসেছিলুম, মনে আছে?”
কথাটার সরাসরি জবাব না দিয়ে একটা শ্বাস ফেলে নন্দলাল বললেন, “আমি একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি হে। এখন সময় নেই। পরে এসো।”
“আজ্ঞে, আমার দরকারটাও বড্ড জরুরি। দাঁড়াবার দরকার নেই, হাঁটতে থাকুন, আমি পিছু পিছু যেতে-যেতেই কথাটা নিবেদন করতে পারব।”
“তুমি সেই ল্যাংড়া শীতলের লোক তো!”
“যে আজ্ঞে। এবার চিনেছেন।”
“দ্যাখো বাপু, আবার যদি পুজোআচ্চার ব্যাপারে এসে থাকো, তা হলে আগেই বলে রাখছি, ও আমি পারব না। অন্য তোক দেখে নাও গে যাও।”
সুধীর বিশ্বাস ভারী বিনয়ের সঙ্গে বলল, “সেবার ভারী অসুবিধেয় ফেলা হয়েছিল আপনাকে, জানি। দক্ষিণা প্রণামীটাও বোধ হয় আপনার পছন্দ হয়নি।”
“সেকথা নয় হে বাপু। দক্ষিণা প্রণামী তোমরা ভালই দিয়েছিলে। গ্রামদেশে কেউ অত দেয় না। কিন্তু আর আমি পারব না।”
লোকটা পিছু ছাড়ল না। শেয়ালের মতো পিছু পিছু আসতে-আসতে বলল, “কথাটা যদি একটু শুনতেন!”
“বলে ফেলল।”
“সেবার তো আপনি নরবলি রদ করে মোষবলি দেওয়ালেন। কাজটা খারাপও করেননি। একটা মানুষকে তো প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন। সেটা আমার পছন্দই হয়েছিল। নরবলিটলি আমিও বিশেষ পছন্দ করি না।”
“ওহে বাপু সুধীরচন্দ্র, তোমাদের হাতে নরবলি একভাবে না হলেও অন্যভাবে হয়ই। কখনও হাড়িকাঠে ফেলে খাঁড়া দিয়ে কাটো, কখনও হয়তো বোমা-বন্দুক ছুরি-ছোরা দিয়ে মারো। নরবলি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। শাস্ত্রমতো নরবলির বিকল্প ব্যবস্থাই করেছিলাম। কিন্তু ওসব আমার সয় না।”
“কিন্তু ঠাকুরমশাই, মোষবলি দিয়েই কি শীতলদার রিষ্টি কাটল? দিন দিন তাঁর শরীর শুকোচ্ছে, দুর্বল হয়ে পড়ছেন, চলতে ফিরতে হাতেপায়ে কাঁপুনি হয়। মোষবলির কথা শুনে আমাদের প্রাণায়াম শর্মা তো খেপে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন!”
“প্রাণায়াম শর্মাটি আবার কে হে?”
“মস্ত জ্যোতিষী। গ্রহ নক্ষত্র তাঁর দশ আঙুলে খেলা করে। সাক্ষাৎ কাঁচাখেকো দেবতা। গনৎকার হিসেবেও চমৎকার। বললেন, আমার দেওয়া বিধান উলটে দিয়েছে, তার ঘাড়ে ক’টা মাথা? তিনি ফের বিধান দিলেন, এবার দুটো নরবলি।”
“দুটো! নাঃ, লোকটা দেখছি ঘোর পাপিষ্ঠ। যাক, তিনি যে বিধানই দিয়ে থাকুন, তোমরা অন্য ব্যবস্থা দ্যাখো।”
“তাই কি হয় ঠাকুরমশাই?”
“খুব হয়। যে-কোনও পুরুতকে নিয়ে যাও। তা ছাড়া আমার এক জ্ঞাতিভাই মারা যাওয়ায় অশৌচ চলছে।”
“ওসব আমরা মানি না। আর অশৌচ হলে কি কেউ খেউরি হয় ঠাকুরমশাই? আপনার দাড়ি তো চকচকে করে কামানো!”
নন্দলাল বিরক্ত হয়ে বললেন, “সে যাই হোক বাপু, তুমি অন্য ব্যবস্থা দ্যাখো।”
“শীতলদাদা এই হাজার টাকা প্রণামী পাঠিয়েছেন। তা ছাড়া দক্ষিণাটাও এবার একটু মোেটারকমেরই দেবেন। রিষ্টিটা না কাটলেই নয় যে ঠাকুরমশাই! প্রাণায়াম শর্মার বিধান যে বেদবাক্য।”
নন্দলাল বললেন, “ওহে বাপু, আর কথা বাড়িও না। বিদেয় হও। নইলে কিন্তু আমি তোক ডাকব।”
ভারী ভয় পেয়ে এবং আরও সরু হয়ে সুধীর বিশ্বাস বলল, “কুপিত হবেন না ঠাকুরমশাই। শুনেছি আপনি শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ। আপনার শাপটাপ লাগলে আমার কি সইবে? তবে আমি একা নই, এই এঁরাও সব আবদার নিয়ে এসেছেন। সবাইকে পায়ে ঠেলা কি ঠিক হবে ঠাকুরমশাই?”
নন্দলাল দেখলেন, সুধীর বিশ্বাসের পিছনে ঝোঁপঝাড় থেকে অন্তত দশ বারোজন দৈত্যের মতো চেহারার লোক নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছে।
নন্দলাল বুদ্ধিমান মানুষ। বুঝলেন, এ সময়ে জেদাজেদি করে লাভ নেই। আপত্তিও টিকবে না।
তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “বাবা সুধীর, তুমি কি পরলোকে বিশ্বাস করো?”
“বলেন কী ঠাকুরমশাই! পরলোকে বিশ্বাস না করে উপায় আছে? ইহলোকটা তো ছ্যাঁচড়ামি করেই কাটল, আমি তো তাই পরলোকের ভরসাতেই আছি।”
“আর ভরসা কোরো না হে। তোমার পরলোকটা বড়ই অন্ধকার।”
দশ-বারোজন লোকে ঘেরাও হয়ে নন্দলাল নৌকোয় এসে উঠলেন। ইষ্টনাম স্মরণ করা ছাড়া তাঁর আর কিছুই করার রইল না।
.
নিজের আশ্চর্য আবিষ্কারের সাফল্যে হলধর নিজেই অভিভূত। বাঁশবনের ভিতরে অন্ধকারে বসে সে কিছুক্ষণ অশ্রুমোচন করল। আনন্দাশ্রুই। বাহবা দেওয়ার মতো কেউ কাছেপিঠে নেই বলে অগত্যা সে নিজেই নিজেকে বাহবা দিয়ে বলল, “না রে হলধর, তোর এলেম আছে বটে! তোর পেটে পেটে যে এত ছিল তা তো কেউ বুঝতেই পারেনি এতকাল! এ তুই যা করলি বাপ, ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কী বুদ্ধি রে তোর! কী ধৈর্য! কী অধ্যবসায়! মানুষের কাছে তুই একটা উদাহরণ হয়ে রইলি। শুধু কি তাই? ইস্কুলে-ইস্কুলে তোর জীবনী পড়ানো হবে একদিন। তোর নামে রাস্তা হবে। কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে তোর ওপর গবেষণা হবে। তোর জন্মদিনের দিন সারা দেশে জন্মজয়ন্তী হবে। না রে হলধর, তুই সামান্য লোক তো নোস…”।
কে যেন বলল, “তা তো নোস বাছা, কিন্তু তোর আক্কেলটা কী? বাঁশবনে বসে ফ্যাচফ্যাচ করে মেয়েমানুষের মতো কাঁদলেই তো হবে না।”
হলধর তাকিয়ে দেখল, একজন বুড়োমতো বিধবা মহিলা সামনে দাঁড়িয়ে আছে।
হলধর ধরা গলায় বলল, “আজ আমার যে বড় আনন্দের দিন বুড়িমা! বেলুনে বেশি ফুঁ দিলে যেমন বেলুন ফুলে ফাটো-ফাটো হয়, আনন্দে আমার সেই অবস্থা। একটু কাঁদলে আনন্দের বাড়তি বায়ুটা বেরিয়ে যায় কিনা।”
“তা আর জানি না বাছা! তেঁতুলছড়া দিয়ে ভাত খেতুম বলে আমারও কি পেটে কম বায়ু হত? উদ্গার তুললে তবে স্বস্তি পেতাম। তা এই বাঁশবনে বসে অন্ধকারে মশার কামড় খেলেই তো হবে না। এবার যে একটু গতর নাড়তে হবে।”
হলধর আপ্লুত গলায় বলল, “আনন্দের ঠেলায় আমার হাত-পা যে বড় অবশ হয়ে পড়েছে বুড়িমা, হাঁটুতে যেন খিল ধরে আছে। এখন কি আর নড়াচড়ার অবস্থা?”
বুড়ি ফোঁস করে উঠে বলল, “তা বলে ঠুটো জগন্নাথ হয়ে উড়ুক্কু কল কোলে নিয়ে বসে থাকবি রে নিমকহারাম? বাড়িতে কী কাণ্ড হয়ে গেল সে খবর রাখিস? রাঘব চৌধুরী না তোর অন্নদাতা? তার দুটো ফুটফুটে ছেলে না তোকে এত বিশ্বাস করে? তাদের বিপদে যদি তোর ওই কল কাজেই না লাগল, তা হলে ভেঙেচুরে উনুনে গুঁজে দিগে যা।”
হলধর শশব্যস্তে বলে উঠল, “কেন, কী হয়েছে বুড়িমা?”
“বলব কী, ভাবলেই আমার হাত-পা হিম হয়ে আসছে। এতগুলো পুষ্যি তোরা, গাণ্ডেপিণ্ডে গিলছিস আর কূটকচালি করে সময় কাটিয়ে দিচ্ছিস! কোন সাহসে অতগুলো ডাকাত ভর সন্ধেবেলা বাড়িতে ঢুকে কচি ছেলেদুটোকে তুলে নিয়ে যায় রে? আস্পদ্দার কথা আরও শুনবি? একটা মর্কট এসে রাঘবকে ভয় দেখিয়ে পাঁচ লাখ টাকা চেয়ে গেছে। না দিলে কী হয় ভাবতেও ভয় করে। এখনও কি হাত-পা জড়ো করে বাঁশবনে বসে থাকতে লজ্জা হচ্ছে না তোর? লজ্জা যদি না হয় তা হলে কাল সকালে পাঁচজনকে মুখ দেখাবি কী করে? লোকে যে তোদের গায়ে থুতু দেবে?”
হলধর অবাক হয়ে বলে, “আজ্ঞে, আপনি কে বুড়িমা? ঠিক চিনতে পারছি না তো!”
“চেনার কি জো আছে বাছা? বায়ুভূত হয়ে থাকি। তবে সম্পর্ক খুব দুরেরও নয়। রাঘবের ঠাকুর্দা ছিল বিচরণ, আমি তার বিধবা পিসি। দেখিস, যেন শুনে আবার ভিরমি খাসনে। ভাল ভেবে নবকেষ্টকে বলতে গেলুম, তা সে চোখ উলটে পঁাত ছরকুটে মুচ্ছো গেল। তাই বলি বাছা, এখন কিন্তু মুচ্ছো টুচ্ছো যাসনে। বড্ড বিপদের সময় যাচ্ছে। মুচ্ছো পেলে চেপে রাখ। পরে সময়মতো মুচ্ছো যাস।”
হলধর তাড়াতাড়ি উবু হয়ে পায়ের ধুলো নিতে গেল। বলল, “আপনি কর্তামশাইয়ের ঠাকুর্দার পিসিমা! কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য!”
“পায়ের ধুলো নিলি বুঝি! তা ভাল। ভক্তিছেদ্দার পাট তো আজকাল উঠেই গেছে।”
“কিন্তু ঠাকুমা, হিসেবমতো আপনার বয়স তো দেড়শো দাঁড়াচ্ছে।”
“তা হবে।”
“এতদিন যে কারও বেঁচে থাকার কথা নয়!”
“দুর বোকা! তা হলে এতক্ষণ কী শুনলি? বেঁচে আছি কে বলল?”
“তবে কি ভূত নাকি আপনি ঠাকুমা?”
“ভূত কথাটা শুনতে বিচ্ছিরি, বরং আবছা মানুষ’ বল।” মাথা চুলকে হলধর বলল, “এ! তা হলে তো মুশকিলেই পড়া গেল! সায়েন্সে তো ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না! বড্ড গণ্ডগোলে ফেলে দিলেন ঠাকুমা।”
“বলি, গণ্ডগোলের কি শেষ আছে রে? যেখানে হাত দিবি সেখানেই গণ্ডগোল। তোর সায়েন্সও থাক, আমরাও থাকি। এখন যা বাছা, লোকজন জড়ো করে বেরিয়ে পড়। বাছাগুলোকে যেখানে নিয়ে গেছে সে হল ময়নামতীর জঙ্গল। ভারী দুর্গম জায়গা। তোর ওই উড়ুক্কু কল ছাড়া যাওয়াও যাবে না।”
হলধর চিন্তিতভাবে বলল, “সে না হয় যাচ্ছি। কিন্তু ঠাকুমা, এই উড়ুক্কু কল পলকা জিনিস। পাল্লাও বেশিদূর নয়। তা ছাড়া ছুঁচোবাজির মতো এদিক-সেদিক চলে যায়।
“ওসব নিয়ে ভাবিসনি। আমি আছি, পীতাম্বরমশাই আছেন, হরু বাবা আছে, পঞ্চা বিশ্বেস আছে। আমরা সব আবছা মানুষ বটে, কিন্তু ক্ষ্যামতা কিছু কম নেই।”
গদগদ হয়ে হলধর বলল, “আর একবার পায়ের ধুলো দিন ঠাকুমা।”
.
সন্ধের মুখে বাড়ির পিছনের পতিত জমিতে তিন-তিনটে মুশকো চেহারার লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হাবু দাসের। তাদের দেখে হাবু দাস ভারী খুশি হল। পথ আটকে দাঁড়িয়ে খুব একচোট হেসে নিল সে।
লোকগুলো নিজেদের মধ্যে একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।
হাবু হেসেটেসে বলল, “খুবই মজার কথা হে! ধরো যদি আমার নাম হয় হাবু, আর পাঁচুর নাম যদি হয় পাঁচু, আর এই বাড়িটা যদি রাঘববাবুর হয়…”
কথাটা শেষ হওয়ার আগেই সামনের লোকটা তার হাতের খেটে ডাণ্ডাটা তুলে ঠাঁই করে হাবুর মাথায় বসিয়ে দিল।
হাবু গদাম করে পড়ে গেল মাটিতে।
কাজের লোক! হু বাবা, এরা যে খুবই কাজের লোক তাতে আর সন্দেহ রইল না গোলাপ রায়ের। বরাবরই সে এইসব কাজের লোককে এড়িয়ে চলে। আজও সে এদের দেখেই ঝোঁপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়েছিল। গা-ঢাকা দিয়েই রইল।
কাজের লোকেরা ফাঁকা পতিত জমিটায় গিয়ে পরপর তিনটে তুবড়িতে আগুন দিল। তুবড়িও বটে! এমন তুবড়ি কখনও দেখেনি গোলাপ রায়। যেমন তেজ, তেমনি বাহার। নানা রঙের ফুলকি যেন ঠেলে দোতলাকেও ছাড়িয়ে গেল। তুবড়ি দেখে দুই ভাই দোতলার জানালায় এসে দাঁড়াতেই কাজের লোকের একজন মোলায়েম গলায় বলল, “তুবড়ি জ্বালাবে খোকারা? এসো না!”
দুই ভাই ছুটে নেমে এল। কাজের লোকেরা চোখের পলকে রুইতন আর হরতনের মুখ দুখানা রুমালে বেঁধে কাঁধে তুলে নিল। তারপর ভারী চটপটে পায়ে গায়েব হয়ে গেল।
খুব সাবধানে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল গোলাপ রায়। চেঁচামেচি করল না। করে লাভও নেই। হাবু দাসকে একটু নেড়েচেড়ে দেখল সে। মাথার চোট খুব গুরুতর নয়। সে কয়েকটা গাদাল পাতা ছিঁড়ে হাতে একটু ডলে নিয়ে হাবুর নাকের কাছে ধরতে কিছুক্ষণ বাদে হাবু চোখ চাইল। তারপর ধড়মড় করে উঠে বসেই হুঙ্কার দিল,”কোথায় সেই শয়তানটা?”
“কার কথা কইছ? শয়তান কি একটা? চারদিকে মেলা শয়তান। গণ্ডায় গণ্ডায় শয়তান।”
“ওই যে শয়তানটা কাল রাতে আমাকে বিছানা থেকে ফেলে দিয়েছিল?”
“যাক বাবা, তুমি তা হলে পুরনো হাবু দাসেই ফিরেছ। পুনর্মুষিক ভব। তা কদম কোঙারকে আধঘণ্টা আগে দেখেছিলাম বটে!”
“কোথায় সে?” বলে উঠতে যাচ্ছিল হাবু।
গোলাপ মাথা নেড়ে বলল, “ব্যস্ত হোয়ো না। সে একজন কাজের লোক। কাজেই এ বাড়িতে এসেছিল, কাজ সেরে ফিরে গেছে। তার নাগাল পাওয়া মুশকিল।”
হাবু গম্ভীর হয়ে বলল, “কিন্তু আমার যে তার নাগাল পেতেই হবে!”
.
সামনের উঠোনে সন্ধে সাতটা নাগাদ মেলা লোক জড়ো হয়েছে। হাবু দাস, গোলাপ রায়, গুণেন সাঁতরা, ভূতনাথ, পাঁচু, নবকৃষ্ণ, খাজাঞ্চি মশাই, হলধর, কে নয়? কারও মুখেই কথা নেই।
হলধর, হাবু আর গোলাপ রায় মিলে শক্ত পাটের দড়ি দিয়ে দুটো লম্বা বাঁশ হলধরের উড়ুক্কু ঝাঁটার সঙ্গে আঁট করে বাঁধছিল।
নবকৃষ্ণ সন্দিহান হয়ে বারবার বলছে, “ও হলধরদাদা, এ জিনিস সত্যিই উড়বে তো! দেখলে বিশ্বাস হয় না।”
হলধর বলল, “ওহে নবকৃষ্ণ, এতে শুধু বিজ্ঞানই নেই, তেনারাও আছেন।”
বিশ্বাস রাঘববাবুরও হচ্ছিল না। তবু সামান্য একটু আশার আলো দেখার চেষ্টা করছিলেন মাত্র। শুধু একবার জিজ্ঞেস করলেন, “আমাকেও যেতে হবে কী?”
হলধর মাথা নেড়ে বলল, “না কর্তামশাই, লোক বাড়িয়ে লাভ নেই। যদি উদ্ধার করা কপালে থাকে তা হলে আমরা তিনজনেই পরব।”
গুণেন বলল, “আমাকেও নিতে পারতে হে! দীপক গেয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আসতাম।”
৭. পালকি চেপে জঙ্গলের ভিতরে
নদী পেরিয়ে আগেরবারের মতোই পালকি চেপে জঙ্গলের ভিতরে দীর্ঘ পথ পার হতে হল নন্দলালকে। জঙ্গলের মধ্যে সেই চাতালেই এসে পালকি নামল।
নন্দলাল নামলেন, চারদিকে যমদুতের মতো চেহারার লোকজন। বেদির ওপর কালীর বিরাট মূর্তি, পুজোর বিরাট আয়োজন চলছে।
নন্দলালের হাত-পা বশে নেই। আগেরবার কৌশলে রক্ষা পেয়েছিলেন। এবার আর তার উপায় দেখছেন না, তবে তার মাথা এখনও পরিষ্কার।
ল্যাংড়া শীতল আগেরবারের মতোই এসে পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, “ঠাকুরমশাই, পুজোটা খুব জোর দিয়ে করবেন। আমার বড় খারাপ সময় যাচ্ছে।”
নন্দলাল স্খলিত কণ্ঠে বললেন, “পুজো না হয় করলুম বাবা, কিন্তু নরবলি-টলি যে আমার সয় না। শেষে যদি রক্তক্ত দেখে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যাই তা হলে পুজোই পণ্ড।
শীতল কঁচুমাচু হয়ে বলল, “নরবলি কি আমিই চাই ঠাকুরমশাই? কিন্তু প্রাণায়াম শর্মা সাফ বলে দিয়েছে, নরবলি না হলে আমার রিষ্টি কাটবে না। দেখছেন তো, দিনদিন আমার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। আজকাল হাত-পা কাঁপে, জোরে হাঁটলে বুকে হাফ ধরে যায়। আগে এক ঠাই বসে দু’সের মাংস খেতে পারতাম, আজকাল তিন পো-র বেশি পারি না। শরীর খারাপ হওয়ায় দলটাও নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে, রোজগার কমছে। প্রাণায়াম শর্মা বলেছেন, নরবলিটা হয়ে গেলেই সবদিক রক্ষে পাবে। মায়ের নাকি এখন পাঠা বা মোষে রুচি নেই। একটু নররক্ত খেতে চান। মায়ের ইচ্ছে হলে কী আর করব বলুন!”
“তা বলে মায়ের কোল খালি করা কি উচিত হচ্ছে বাপু? ওটাও যে ঘোরতর পাপ!”
“কিন্তু আমাকেও তো বাঁচতে হবে ঠাকুরমশাই। এতগুলো লোক আমার মুখপানেই চেয়ে আছে।”
নন্দলাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।
একটু বাদেই পাঁচ-সাতটা লোক এসে ধড়াস ধড়াস করে দুটো মুখবাঁধা বাচ্চা ছেলেকে বেদির কাছাকাছি মাটিতে ফেলল। মশালের আলোয় নন্দলাল দৃশ্যটা দেখে শিহরিত হলেন। ছেলে দুটোকে ভারী চেনা-চেনা ঠেকছিল তার।
সুধীর বিশ্বাস এগিয়ে এসে ভারী আহ্লাদের গলায় বলল, “চিনতে পেরেছেন তো ঠাকুরমশাই?”
“কে বলো তো বাপু?”
“কেন, রাঘববাবুর দুই ছেলে রুইতন আর হরতন!”
নন্দলাল হঠাৎ বুকে প্রচণ্ড একটা ব্যথা টের পেয়ে চোখ বুজে ফেললেন। হার্ট ফেল হয়ে যাবে কিনা বুঝতে পারলেন না। গেলেই ভাল। এই পঙ্কিল পৃথিবীতে আর বেঁচে থাকার প্রয়োজনই বা কী?
খ্যাক খ্যাক করে একটু হেসে সুধীর বিশ্বাস বলল, “এবার এক ঢিলে দুই পাখি, বুঝলেন ঠাকুরমশাই?”
“না, বুঝলুম না।”
“নরবলিকে নরবলি, তার ওপর মুক্তিপণ বাবদ পাঁচ লাখ টাকা আদায়।”
“শিরে বজ্রাঘাত হবে যে হে!”
“বজ্রাঘাতের কমও হচ্ছে না ঠাকুরমশাই। ল্যাংড়া শীতলের রিষ্টির জন্য আমাদের যে হাঁড়ির হাল। আগে হেসেখেলে মাসে দশ বিশ হাজার টাকা আসত পকেটে। এখন দু-তিন হাজারের বেশি নয়। পাঁচ লাখ এলে খানিক সুসার হয়।”
ছেলে দুটোকে দেখে চোখ ফেটে জল আসছিল নন্দলালের। এদের জন্মাতে দেখেছেন। অসহায় বাচ্চা দুটো দীর্ঘ পথের শ্রমে ঘুমিয়ে পড়েছে।
“বাপু, সুধীর।”
“আজ্ঞে।”
“ওদের বদলে আমাকে বলি দিলে হয় না?”
“তা কি আর হয় না? কিন্তু তা হলে উচ্ছ্বঘ্ন করবে কে? ঠাকুরমশাই, মায়াদয়া কি আর আমাদের মধ্যেও নেই? তবে কিনা, চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা। জন্ম-মৃত্যু কি আমাদের হাতে, বলুন!”
নন্দলাল বিড়বিড় করে বললেন, “তোমার মৃত্যুটা আমার হাতে থাকলে বড় ভাল হত।”
“কিছু বললেন ঠাকুরমশাই?”
“না হে। ইষ্টনাম জপ করছি।”
“হ্যাঁ, হ্যাঁ, কষে ইষ্টনাম করুন তো। দুনিয়াটা পাপে যে একেবারে ভরে উঠল ঠাকুরমশাই। ইষ্টনাম হচ্ছে বঁটার মতো, পাপ-তাপের জঞ্জাল সব ঝেটিয়ে সাফ করে দেয়। বেশ চেপে ইষ্টনামটা চালিয়ে যান।”
বকরাক্ষসের মতো নকুল সর্দার গাছতলায় বসে একটা শিরীষ কাগজে খাঁড়ার ধার তুলছে। মুখে একটা লোল হাসি। নরখাদকই বটে। মাঝে-মাঝে চোখ তুলে যখন এধার-ওধার তাকাচ্ছে তখন ওর চোখ থেকে যেন একটা ঝলকানি বেরিয়ে আসছে। কেন যে নকুল সর্দার নাম ভাঁড়িয়ে রাঘব চৌধুরীর বাড়িতে ঢুকেছিল তা এখন খানিকটা বুঝতে পারছেন নন্দলাল। এদের কাজ খুব পাকা। বাড়িতে লোক ঢুকিয়ে পাহারার ব্যবস্থা কেমন, লড়াই দিতে পারবে কি না, রাস্তা আছে কি না তা জেনে নিয়ে তবে কাজে নেমেছে। রাঘবের বাড়ি হল খোলা হাট, সেখান থেকে ছেলে চুরি করা কোনও কঠিন কাজ নয়।
একটা দানো এসে হাতজোড় করে বলল, “ঠাকুরমশাই, আর দেরি হলে যে লগ্ন পেরিয়ে যাবে।”
“এই যে বাপু, যাচ্ছি। হাতপায়ের কাঁপুনিই যে থামতে চাইছে না হে।”
‘ভয় পাবেন না ঠাকুরমশাই। পুজোটা হয়ে যাক, তারপর সারারাত বিশ্রাম করার সময় পাবেন। পুরু গদিওলা বিছানা করে রাখা হয়েছে আপনার জন্য।”
নন্দলাল জপ করতে করতে শান্ত হলেন। হাতমুখ ধুয়ে পুজোর আসনেও বসলেন। চারদিকে ঢাক ঢোল কাঁসি বাজছে। নন্দলাল মন্ত্র-ট ভুলে খুব তাড়াতাড়ি একটা মতলব আঁটছিলেন। কিন্তু জুতমতো কোনও মতলবও আসছে না মাথায়। দুঃখে ক্ষোভে বারবার চোখে জল আসছে।
“বলি ওহে নন্দ!”
নন্দলাল বোজা চোখ খুলে অবাক হয়ে চারদিকে তাকালেন। ঠিক তাঁর গা ঘেঁষে পিছনে একজন বুড়োমানুষ উবু হয়ে বসা। পরনে মোটা আটহাতি ধুতি, গায়ে বেনিয়ান, সাদা ছুঁড়ো গোঁফ, মাথায় কাঁচাপাকা চুল।
নন্দলাল অবাক হয়ে বললেন, “আপনি কে?”
“আমি হলুম পীতাম্বরমশাই। রাঘব চৌধুরীর ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ।”
নন্দলালের গায়ে কাঁটা দিল। “ঘাবড়ে যেও না। পুজোটা একটু সময় নিয়ে করো।”
“যে আজ্ঞে। বড় বিপদ যাচ্ছে পীতাম্বরমশাই।”
“বিপদ বলে বিপদ! তবে ভরসা রাখো৷ পুজোটা চালিয়ে যাও। ওরা তাড়া দিলে বোলো, এ বড় সাঙ্ঘাতিক পুজো। কোনও অঙ্গহানি হলে উলটো ফল ফলবে। আর কিছু ভয় না পাক, পুজোআচ্চাকে খুব ভয় পায়।”
“উপায় হবে বলছেন!”
“না হলে দেড়শো বছরের আলিস্যি ঝেড়ে কি এতদুর ছুটে আসতুম হে? দিব্যি শুয়েবসে সময় কাটছিল, ঝামেলা পাকিয়ে ওঠায় এই দৌড়ঝাঁপের মধ্যে পড়েছি।”
হঠাৎ একটা বাজখাঁই গলা বলে উঠল, “এই যে পুরুতমশাই, পুজো আর কতক্ষণ চলবে? বলিটা দিয়ে না ফেললে কোথায় আবার কী বাধা পড়ে কে জানে!”
পিছনপানে চেয়ে নকুল সর্দারের হাতে লকলকে খাঁড়াটা দেখে চোখ বুজে ফেললেন নন্দলাল। তারপর হঠাৎ বেশ রাগের গলায় বললেন, “দিলে তো মন্তরে একটা বাধা! আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। বলি এ কি ছেলের হাতের মোয়া নাকি হে! কাঁচাখেগো দেবতা বলে কথা! একটু এদিক-ওদিক হলে রক্ষে আছে? যাও যাও, এখন আমাকে বিরক্ত কোরো না।”
নকুল একটু মিইয়ে গিয়ে বলল, “আহা, বলিটা আগেভাগেই হয়ে যাক না। তারপর সারারাত পুজো চালিয়ে যান, ক্ষতি নেই!”
“তা হলে বাপু, তুমিই বরং পুজোয় বোসস। আমি উঠছি।”
ল্যাংড়া শীতল একটু দূরে বসে ছিল। পেল্লায় একটা ধমক মেরে বলল, “অ্যাই নোকলো! তোর অত সর্দারির দরকার কী? পুজোআচ্চার কিছু বুঝিস?”
নকুল একটু দমে গিয়ে বলল, “এই পুরুতটা একটু খিটকেলে আছে।”
“না, না, এ ভাল পুরুত। সবাই বলে নন্দঠাকুর পুজো করলে ভগবান যেন কথা কয়।”
নকুল তার জায়গায় গিয়ে বসল। নন্দলাল হাঁফ ছাড়লেন।
কে একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, “আকাশে ওটা কী উড়ছে বলে তো? শকুন নাকি?”
আর একজন বলল, “কখনও শুনেছিস রাতে শকুন ওড়ে। অন্ধকারে দেখলিই বা কী করে?”
“আমি যে অন্ধকারেও দেখতে পাই। না, পাখি-টাখি নয়, তার চেয়ে বড় জিনিস।”
সবাই উধ্বমুখে কিছু একটা দেখছে। নন্দলাল তাকালেন না। কে জানে কী। তবে যাই হোক, ভগবানের আশীর্বাদে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠলে ভালই হয়।
আর একজন চেঁচিয়ে বলল, “আমিও দেখতে পাচ্ছি। ওটা বোধ হয় একটা এরোপ্লেন।”
“দুর গাধা। এরোপ্লেন হলে শব্দ হবে না?”
“তাও তো বটে!” একে একে সবাই দেখতে পেল। একটা গুঞ্জন আর চেঁচামেচিও ছড়িয়ে পড়তে লাগল।
“উরেব্বাস! এ যে লম্বা একটা জিনিস। তাতে কী যেন আছে। চক্কর মারছে।”
গভীর বিকট গলায় ল্যাংড়া শীতল হাঁক মেরে বলল, “সবাই অস্তর হাতে নে। খুব হুঁশিয়ার! একটা ষড়যন্ত্র আছে বলে মনে হচ্ছে।”
নন্দলাল হঠাৎ আর্তনাদ করে বললেন, “সর্বনাশ! ও কাজও কোরো না হে! পুজোর মন্ত্র দেবতাদের পায়ে পৌঁছলে তাঁরা সব পুষ্পক বিমানে যজ্ঞস্থলে এসে হাজির হন। অস্ত্র দেখলে কুপিত হবেন। ওসব লুকিয়ে ফেলো।”
দানবেরা মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল। শীতল বলল, “কোনও বিপদ নয় তো ঠাকুরমশাই?”
“আরে না। আজ পুজো সার্থক হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র সব দূরে ফেলে দিয়ে হাতজোড় করে বসে আমার সঙ্গে সঙ্গে স্তব করতে থাকো। না হলে সব পণ্ড হবে।”
ডাকাতরা ফাঁপরে পড়ে গেল। ঠিক বিশ্বাসও করছে না, আবার দোটানাতেও পড়েছে।
শীতলই হুকুম দিল, “ঠাকুরমশাই যা বলছেন তাই কর রে তোরা।”
সবাই ঝপাঝপ অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিল। তারপর করজোড়ে স্তব করতেও বসে গেল। নন্দলাল তাদের তাণ্ডব স্ত্রোত্র পাঠ করাতে লাগলেন। যদি সত্যিই কেউ বা কিছু এসে থাকে, তবে তাদের নিরাপদে নেমে আসা দরকার। তাণ্ডব স্তোত্র লম্বা জিনিস। সময় লাগছিল।
ঠিক এই সময়ে সাঁই সাঁই শব্দ করে হলধরের উড়ুক্কু বঁটা তিন মূর্তিমানকে নিয়ে নেমে এল। হাবু দাস লাফ দিয়ে নেমেই চিৎকার করে উঠল, “কই, কোথায় সেই শয়তানটা?”
গোলাপ রায় অবাক হয়ে বলে, “এখানে শয়তানের অভাব কী গো হাবুদাদা? এ তো শয়তানের একেবারে হাট বসে গেছে! তুমি যাকে খুঁজছ সে ওই যে গাছতলায় খাঁড়া হাতে বসে আছে।”
হাবু দাস চোখের পলকে একটা ঘূর্ণিঝড়ের মতো গিয়ে নকুল সর্দারের ওপর পড়ল। নকুল বিস্ময়ে হাঁ করে ছিল। ওই হাঁ নিয়েই পর পর দুটো রদ্দা খেয়ে জমি ধরে নিল।
তারপর যে কাণ্ড হতে লাগল তা অবিশ্বাস্য। দানোরা কেউ হাত তোলারও সময় পেল না। হাবু-ঘূর্ণিতে তারা খড়কুটোর মতো উড়ে যেতে লাগল।
তারপর গদাম গদাম করে ছিটকে ছিটকে পড়তে লাগল এখানে সেখানে।
শীতল পালানোর চেষ্টায় ছিল। হাবু তার ঠ্যাং ধরে তুলে কয়েকবার ঘুরিয়ে পাক মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। শীতল অজ্ঞান হয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো চুপটি করে পড়ে রইল।
লড়াই শেষ।
.
হলধরের উড়ুক্কু বঁটাকে কয়েকবার খেপ মারতে হল। প্রথম খেপে বাড়ি ফিরল রুইতন আর হরতন। একে একে ঠাকুরমশাই নন্দলাল, গোলাপ রায়, হাবু দাস। এবং সেইসঙ্গে অচেতন কদম কোঙার ওরফে নকুল সর্দারও।
নন্দলাল আতঙ্কিত হয়ে বললেন, “ওরে ওটাকে এনেছিস কেন? ও যে সব্বোনেশে লোক!”
হাবু বলল, “বহুকাল পরে লড়াই করে গায়ে হাতে বড্ড ব্যথা হয়েছে মশাই। তাই এটাকে নিয়ে এসেছি। হাত পা টিপে দেবে। ভয় পাবেন না। এর ওষুধ আমার জানা আছে।”
তা কথাটা মিথ্যেও নয়। দেখা গেল, নকুল সর্দার আর আগের মতো নেই। ভারী ভালমানুষ হয়ে গেছে সে। হাবুর গা-হাত-পা টিপে দেয়। তার কাছে কুস্তির প্যাঁচও শেখে, ফাঁইফরমাশ খাটে।
চোখের চাউনিটা একদম গরুর মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।
এ বাড়িতে এখন প্রায়ই আন্নাকালী দেব্যা, পীতাম্বরমশাই, আর পঞ্চা বিশ্বাসকে দেখা যায়। কেউ ভয় পায় না বটে, তবে আন্নাকালী দেব্যার শাসনে এখন আর অনাচার হওয়ার জো নেই। দু’বেলা গোবরছড়া গঙ্গাজল দিতে হয় বাড়িতে, তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বলে, শাঁখে ফুঁ।
হলধরের উড়ুক্কু ঝাঁটায় চেপে আজকাল রাঘব বিকেলে বেড়াতে বেরোন, নন্দলাল মাঝে মাঝে যজমান বাড়ি যান, রুইতন আর হরতন বন্ধুদের নিয়ে হইচই করে চড়ুইভাতি করতেও যায়।
লোকমুখে শোনা যায়, ল্যাংড়া শীতলের দল ভেঙে গেছে। শীতল সাধু হয়ে গেছে। দু-চারজন বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে মাধুকরী করে বেড়ায়, কেউ চাষবাসে মন দিয়েছে, কেউ যাত্রার দলে নাম লিখিয়েছে।
তা সে যাই হোক, মোট কথা, হাট গোবিন্দপুরে এখন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করছে।
(সমাপ্ত)

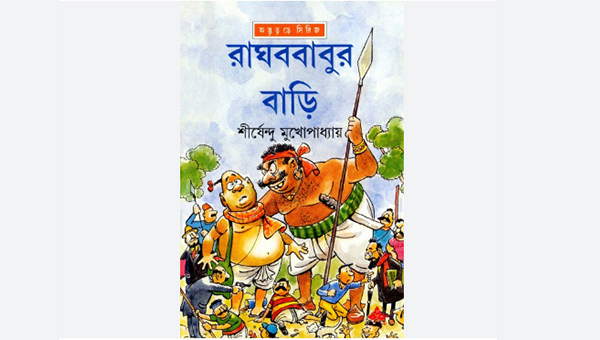





Post a Comment